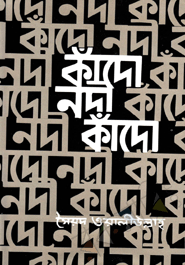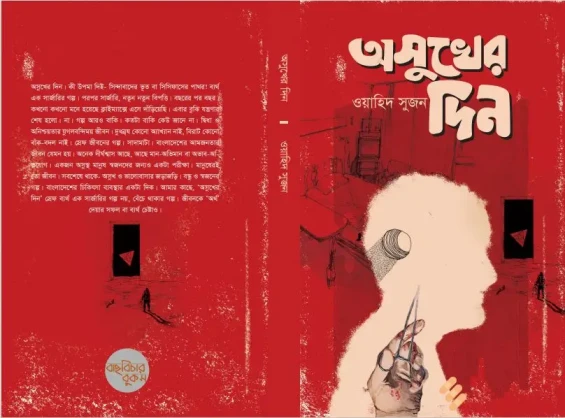এক.
১৯৬৮ সালে প্রকাশিত ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (আগস্ট ১৫, ১৯২২-অক্টোবর ১০, ১৯৭১) তৃতীয় ও শেষ উপন্যাস। বিখ্যাত লেখকের বিখ্যাত এই উপন্যাসের এমনই ধারা- উদ্বেগসঙ্কুল পাঠকদের খুবই উদ্বেগের মধ্যে রাখে। অথবা পাঠকদের আপন আপন জীবন আর তার অনিশ্চিত বিস্তৃতি নিয়ে উদ্বেগসঙ্কুল করে তোলে। তাই, ক্ষীণকায় এই উপন্যাস পড়া চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। নিত্য আহজারিতে দেহ-মন আপ্লুত করে। উপন্যাসের তাবৎ চরিত্র, এমনকি প্রকৃতিরও। পাঠকের তরফে বলি- কী এক গুরুভার যেন কাঁধে চেপে বসে। সে ভারটা নামিয়ে কিছুটা স্বস্তি পেতে চায়, কিন্তু ভারটা কাঁধে না থাকলেও কী এক অস্বস্তি। উপন্যাসের পাতায় বার বার পাঠককে টেনে নিয়ে যান ওয়ালিউল্লাহ। এই হলেন ‘কাঁদো নদী কাঁদো’র সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ। উপন্যাসটি বিশেষ এই পাঠকের মনে যে যে ভাবের উদয় ঘটিয়েছে তার বিবরণ দেয়া যাক। বলাবাহুল্য সে বিবরণ পাঠকের কলবের মতো এবড়ো-খেবড়ো। সে কারণে অনুমান করে বলা যেতে পারে সংশ্লিষ্ট অপরাপর বিষয়-আশয় হাজির হবে হয়তো।
শুরুতে কিছুটা স্মৃতিপাঠ হোক! একই অস্বস্তি টের পাওয়া যায় তার দ্বিতীয় উপন্যাস ‘চাঁদের আমবস্যা’য়, এটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর আগের কথা। তবে সেই বইয়ের শেষ ৫-৬ পৃষ্ঠা পড়তে পারিনি। বইটা সংগ্রহে থাকা সত্ত্বেও অবস্থান বদলের কারণে আর মনোনিবেশ করা হয়নি। তার মানে এই নয়, পাঠকের আগ্রহ জারি ছিল না। মানব মনের বিচিত্র খেয়াল হয়তো বইটি আর হাতে নেয়া হয়নি। কিন্তু দিনে দিনে এই ধারণা পোক্ত হয় যে, সে উপন্যাসের নায়ক শেষ পর্যন্ত ভব যান্ত্রণা জুরিয়েছেন। সে কল্পিত শোকেও মন আর্দ্র হয়েছিল। হয়তো লেখকের কপালে নিন্দাও জুটেছে। ওয়ালীউল্লাহ্্র টেনে আনা উদ্বেগ কেন যেন মৃত্যুকে ভালো উপসংহার হিসেবে সুপারিশ করে! কিন্তু পরে জানা গেল উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মারা যাননি। ভার কিছুটা লাঘব হলো। যদিও তার বেঁচে থাকার বিড়ম্বনাও কম নয়। সে বিড়ম্বনা পাঠকের জন্য কম শোকের নয়।
মোটামুটি অন্যসব ওয়ালীউল্লাহ পাঠকের মতো ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত তার প্রথম উপন্যাস ‘লালসালু’ প্রথমে পড়েছি। শুনে আসছিলাম তার লেখায় অস্তিত্ব সঙ্কটজনিত উদ্বেগ নাকি গাঢ়। লালসালুর মজিদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কম নয়। সেই উদ্বেগ মজা মতো টের পাওয়া গেল পরের দুইখান উপন্যাসে। আলোচকরা জার্মান-ফরাসি বাহিত অস্তিত্ববাদের (এক সাধারণত কন্টিনেন্টাল ফিলোসফিতে ফেলা হয়, যা ইংরেজিভাষী দর্শনের বাইরে) সঙ্গে জুড়ে দেন এই উপন্যাস দুটিকে। ভাগ্যের ফের শেষ জীবনে ওয়ালীউল্লাহ ফরাসি দেশেই ছিলেন। সেখানেই শুয়ে থাকবেন কেয়ামত তক। অস্তিত্ববাদের সঙ্গে দুঃখ-ভারবহনের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে। সেটা নিখাদ অনিশ্চয়তাজনিত কী! যেহেতু কোনো সারবস্তু ব্যক্তির পূর্বগামী না। অর্থাৎ সবকিছু ব্যক্তির পরের এবং পরের বিষয়। আমরা যারা জীবনের আগে নানা সারবস্তুর কথা চিন্তা করছি এবং বুক চাপরাই তাদের জন্য বিষয়টা অনেকটা শূন্যের মাজারে খাবি খাওয়ার মতো। প্রশ্ন করতে পারেন তা সত্ত্বেও ওয়ালীউল্লাহ্্ কেন পাঠককে টেনে রাখেন।
উপন্যাসে ওয়ালীউল্লাহ এমন ধারার বিবিমষা অহরাত্রি বজায় রাখেন। তা কতখানি মহৎ-মহত্ত্বের ধারণা ছাড়া ভাসা ভাসাভাবে বলা সম্ভব না। অন্তত সাহিত্যের মহত্ত্বের বোঝাপড়া তো লাগে। মহত্ত্বের সঙ্গে দুঃখের সম্পর্ক বিরল নয়।
সেসব বাদ দিয়ে সাধারণ বিষয়-আশয় নিয়ে বলা যাক। লালসালু’তে যাও হাসার মতো মানুষ দুই-একজন পাওয়া যায় (অবশ্যই হাসি-ঠাট্টা সেখানে অপরাধের পর্যায়ে পড়ে) স্মৃতি বলে অন্য দুটি উপন্যাসের মানুষ হাসে না, তাদের মনে কোনো আনন্দ নাই। কিন্তু কেন নাই? অথবা অন্য দিক থেকে বলা যায় সেখানে মানুষের আগে আনন্দ বলে কোনো সার পদার্থ নাই। কিন্তু পরেও কি কিছু থাকে না? তারপরও এটা তো সত্য এইসব দুঃখ-উদ্বেগ আমাদের এই জগতেরই বিষয়। ফলে, ওয়ালীউল্লাহ্্ যতই উদ্বেগে রাখেন না কেন সে উদ্বেগ আসলে জারি থাকে না। পাঠকের নিত্য অভিঘাতে যা ধরনা দেয়_ তা হলো এই জগতে নাকি মানুষ আগুনের উপরে বসেও পুষ্পের হাসি হাসে! হয়তো ওয়ালীউল্লাহ উপন্যাসে ফুলের বাগানও নেই। ফুলের সঙ্গে হাসি-আনন্দের মাখামাখি আছে বটে!
স্মৃতিভ্রষ্ট না হলে এটাও বোধহয় যে, শেষ দুইটা উপন্যাসে কেউ গান গায় না_ এমনকি দুঃখের গানও না। ‘কাঁদো নদী কাঁদো’র নদীর বিলাপকে গান বলা যেতে পারে। কেননা সেখানে সুর আছে, তাল আছে, লয়-বিলয় আছে। তবে নৃত্য নেই। বিচিত্র রকমের সে সুর উপন্যাসের সব ঘটনাকে ছাপিয়ে বেজেই চলে। কিন্তু বৃহত্তর অর্থে সাংস্কৃতিক বিষয়-আশয় বলে যে জিনিসটা বুঝি, মানে ব্যাখ্যা করতে না পারলেও কিছু একটা যে আমাদের জড়িয়ে রাখে মনে হয়_ তার হদিস নেই। সে অর্থে ধর্ম নাই_ কিছু অর্থে তো আছে!
কথা শুধু নাই নাই করে আগাচ্ছে। নাই মানে নেতি না। কি নাই তার তালিকা করলে কি আছে তা নিয়েও ধারণা হয়। নাই মানে না থাকার সমস্যা তা না। তবে এমন হতে পারে বিশেষ করে মোটিভ ধরে মানুষ, সমাজ বা সভ্যতাকে চেনার জন্য এগুলোর জরুরত নেই। পেছনে একটা দার্শনিক অবস্থান থাকতে পারে। নানা কিছুর মধ্যে এটাও হতে পারে- অনুপস্থিতিই উপস্থিতির স্বাক্ষর। অথবা আমাদের মন বলে না থাকা জিনিসগুলো গৌণ বলে গণনায় আসেনি। কোনো কিছু গৌণ হওয়া মানে তার অনুপস্থিত নয়- কখনও কখনও অন্তরালের প্রেরণা হতে পারে। অথবা সমাজের কোনো কিছুর উজ্জ্বল উপস্থিতিকে অস্বীকার করা ব্যক্তির মনস্তাত্তি্বক কাঠামোকে একটা জালের মধ্যে পোরা যায়, যদিও আর যা যা অনুপস্থিত তাতেও ব্যক্তির স্বাক্ষর থাকে। আবার সঙ্কীর্ণতাও হতে পারে অথবা বৃহত্তর কোনো অর্থ। ওয়ালীউল্লাহ্্ এসব কোনোটায় না-ই করতে পারেন। কিন্তু এসবের বিলয় মানে পাঠকের মনে বিলয় নয়। বরং, তার মনের মধ্যে এর জন্য খাঁ খাঁ ভাব বিরাজ করতে পারে। অথবা উপন্যাসের চরিত্রগুলোর। সেটা আমরা জানি না। আমরা জানি না তার কী চায়, কেন চায়। কিছু একটা চায় কী? তারপরও পাঠক নিজের মতো করে অনুমান জারি রাখে। জারি থাকুক।
কিন্তু না থাকার ভেতর দিয়েও উপন্যাসটা পড়া যায়। আগের কথাগুলো বলা গেল এই একটা কারণে। যেটা প্রথমে বলছিলাম। ওয়ালীউল্লাহর লেখায় পাঠককে টেনে নেয়ার ক্ষমতা আছে।
দুঃখকে কেউ কেউ মৌলিক অনুভূতি বলেছেন। যদিও আধুনিকতায় আশ্রয় পাওয়া দুঃখবোধ অনেকটা খ্রিস্টিয় বিষয়াদির মতো। নিরস, কালো, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একটা ব্যাপার কিন্তু বিনোদনমূলক। অনেক আর্ট ফিল্মের মতোও কী! উপমহাদেশে দুঃখের দর্শন দিয়েছেন গৌতম বুদ্ধ। তার স্বরূপ একদম আলাদা। তিনি জগৎকে দুঃখময় বলে ক্লান্ত হননি, এরপর বলেছেন দুঃখের নিদান আছে। তার এই দর্শন যতটা প্রত্যয়ে সীমাবদ্ধ তার চেয়ে বেশি প্রত্যয়কে উতরে দিয়ে জীবনের নতুন একটা সীমা অঙ্কনে। তাই বুদ্ধের মহত্ত্ব শূন্যতায় খাবি খায় না। কিন্তু শিল্পের যে অঞ্চলে যে খ্রিস্টাব্দ হাজির, তা শুধু আত্মোৎসর্গের অলীক বেদনা নিয়ে হাজির।
যে কথা হচ্ছিল, ওয়ালীউল্লাহ দুঃখের একটা পেন্ডুলাম কেমন করে যেন ঝুলিয়ে রাখেন। ফলে উপন্যাস পড়াকালে এবং পড়ার বিরতিতে পেন্ডুলামটি অবিরত এদিক-ওদিক নড়ে। পড়ার বিরতিতে যেন আরও জোরে নড়ে। পাঠক তার ধক্ষনি শুনতে চায়। এই যে নিরাশার ভেতরও মানুষ কি যেন তালাশ করে (সুখের কথা বলব না, এ বস্তু সেখানে নেই) অথবা কিছু না হওয়ার মধ্যেও মানুষ কি যেন তালাশ করে অথবা মানুষকে তালাশ করতে হয় এমন একটা ভাব তিনি জাগিয়ে তোলেন। কিন্তু এর গড়ফল শূন্যই মনে হয়। যদিও এই বচনের সমস্যা হলো এখানে মানুষের আগে একটা সার চলে আসছে। কিন্তু পাঠক তো সেই উপন্যাসে বসে নাই। বসে না থেকেই বলছি জীবনকে একটা গুরুতর ঘটনা করে তুলে তবে পাঠকরে সওয়ার করার গুণ বিরল। বিরল এই অর্থে যে, তার বুননের ভেতরে এমন জিনিস আছে, যার মধ্যে অমাদের তালিকা থেকে অনেক কিছু বাদ গেলেও আমাদের বলে আপন করে নেয়ানোর ক্ষমতা তার আছে। তাকে আলগা ভাবারও সুযোগ হয় না। এই দ্বৈরথ থেকে রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর কবিতার মতো বলা যায়_ ‘এ কেমন ভ্রান্তি আমার’!
হে মধুর ভ্রান্তি! ডাকিব তোমায় জনম জনম।
দুই.
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও তার কাজ নিয়ে যতটুকু লেখালেখি পড়েছি তাতে মনে হয় এটা স্বীকার্য হয়ে গেছে- বাংলাদেশের উপন্যাস লেখকদের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্য। তার লেখার যে ধাঁচ তা অনুসরণীয় হওয়ার যোগ্যতা রাখে। অথবা অন্যভাবে বললে ইতিহাসে এর ধারাবাহিকতার রেশ থাকার কথা। থাকার অনুমান এই অর্থে যে তার গল্পের বুননে সহজ একটা ভাব আছে, সে ভাবের মধ্যে তিনি পদ্ধতিগতভাবে মানুষের অন্দরমহলের তত্ত্ব তালাশ করেন। পাঠক সেটা চায় বলে সঙ্গে সঙ্গে বুঝি অনুরণনিতও হয়, যা উপন্যাসের ভাষার ভালো উদাহরণ হতে পারে। তাছাড়া এটা এই অঞ্চলে লেখা প্রথমদিকের উপন্যাসগুলোর একটা। শুধু প্রথমদিকের লেখা হিসেবে নয়, এর বিষয়নিষ্ঠতা ও লিখনরীতির জন্য তো বটে। তাই ওয়ালীউল্লাহ অর্জন নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। যৎকিঞ্চিত যা পড়ছি তার মধ্যে তো অনন্যতা বজার রাখছেন বলেই মনে হয়। নাকি! আমার মনে হয় সে ধারাবাহিকতা আমরা খুঁজলে কিছুটা পাওয়া যেতেও পারে।
এতে দুটো বিষয় লেপটে থাকতে পারে- ভাষা কাঠামো ও যে রাজনৈতিকতা তার ধারাবাহিকতা। এখানে আমরা একটা উদাহরণে যেতে পারি। ‘চাঁদের অমাবস্যা’ পড়াকালে শহীদুল জহিরের ‘ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প’ এই নামটার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। নামটা মিষ্টি মনে হয়েছে, শেষে জানা গেল তার সব রচনার নামই মিষ্টি। ওয়ালীউল্লাহ্্র দেয়া নামগুলোও বেশ মিষ্টি। কিন্তু জহিরের কোনো বই পড়া হয় নাই তখনও। পরে তিনটে উপন্যাস ও কয়েকটা গল্প পড়েছি। ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ পড়াকালে যেন খুব স্বাভাবিকভাবেই হাজির হলেন শহীদুল জহির। তিনি যেন নায্য হিস্যার তাগিদে হাজির হলেন। ওয়ালীউল্লাহ গদ্যরীতি ও দর্শন তাকে ডেকে নিয়ে আসছে। ডাকবেই বা না কেন, পাঠকের অনুমান ক্রিয়া বলল, শহীদুল জহির এক দিক থেকে ওয়ালীউল্লাহ্্র এঙ্টেনশন। তবে সেটাকে এগিয়ে যাওয়া বললে হয়তো ভুল হবে। জহির নিজের কিছু অর্জন নিয়ে হাজির। যেমন- তিনি জাদু বাস্তবতাময় ভঙ্গি, হিউমার ও নাটুকেপনার মধ্য দিয়ে বাংলা উপন্যাস ও গল্পে পথ করে নিয়েছেন_ অবশ্য আলাদাভাবে। বিনোদন আছে তবে স্বস্তি নেই আরকি! এটাও নানা কারণে বাংলা উপন্যাস ভুবনে আলোচনার পরিসর দাবি করে। এ লেখায় সুযোগ নেই বটে। তবে ধারাবাহিকতার প্রসঙ্গে এভাবে বলা যায়, শহীদুল জহিরকে এখন অনেকে অনুকরণের চেষ্টা করেন। সেটা অনেকটা ব্যর্থও বটে। সম্ভবত এখানে এগিয়ে নেয়া বা নিজের জন্য পথ করার বিষয়টা নেই। ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে নিজের পথটা কীভাবে করে নিতে হয় জহির তার ভালো উদাহরণ। সে চেষ্টা করা যেতে পারে!
দুজনের কাজের মধ্যে একটা রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা আছে বলে মনে হয়। ওয়ালীউল্লাহ লেখালেখির শুরু ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ভাগ হওয়ার আগে থেকে। সে সময় এখানকার মুসলমানদের দুই-এক ঘর পশ্চিমা শিক্ষার আলোয় নিজেদের ফর্সা করতে শুরু করেছেন। যাকে ভারতীয় উপমহাদেশের ইংরেজি শেখার সঙ্গে মিশিয়ে দেখা যেতে পারে। এখানের ইংরেজি শিক্ষার ফল কতটা এই অঞ্চলের বাইরে আবেদনময় হয়ে উঠতে পেরেছে তাও প্রশ্ন। বরং, ঘটনা বিচার করলে মনে হয়, পশ্চিমের কয়েক শতকের ইতিহাস যেন লহমায় এখানে ঢুকে গেল। এছাড়া লোকে বলে, এই অঞ্চলে এর আগে যুক্তি-বুদ্ধির ব্যবহার ছিল না! ফলে সে শিক্ষা এখনকার সমাজকে দেখার নতুন বীক্ষা দেয়। আবার রাজনীতি পরিগঠনে নতুন ধাঁচ তৈরি করে। এটাকে হিসাবের বাইরে রেখে বলা যায়, ওয়ালীউল্লাহ কাজের মধ্যে সেই শিক্ষার ছাপ উপস্থিত। সেই শিক্ষার সঙ্গে লোক মানসের সম্পর্ক কতটা থাকল সেটাও প্রশ্ন। তার চেয়ে বড় দিক হলো সমাজকে কোন চোখে দেখা হবে। সে সময়ে শিক্ষিত হয়ে ওঠার ইতিহাসের একটা সাধারণ প্রবণতাকে আমরা এখানে পাব। খুবই জনপ্রিয় উদাহরণের সাহায্য নেয়া যাক। ওয়ালীউল্লাহ্্ এক ধর্মকে কীভাবে চিত্রায়িত (কেননা, ধীরে ধীরে এটি বড় প্রশ্ন আকারে হাজির হয়) করে তা থেকেও স্পষ্ট। যা পশ্চিমার্থে কোনোভাবে ধর্মের পর্যালোচনা বলা চলে না। বরং, কলকাতার ইংরেজি শেখার মধ্য দিয়ে যে ধরনের চিন্তা (যাকে রেনেসাঁও বলা হয়) গড়ে উঠেছে তার রেশ স্পষ্ট। অবশ্য আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞান-যুক্তির নামে বিপরীত কোনো ঘটনা যে ঘটেনি, তা নয়। একইভাবে মানুষ ও সমাজকে ব্যাখ্যার দিকটাও। সে সময় ইংরেজি শিক্ষিতের হাতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে এটি তাদেরই ব্যাখ্যা। ওয়ালীউল্লাহ্্ তার বাইরে যাননি।
অন্যদিকে শহীদুল জহিরের সুলিখিত জাদু বাস্তবতার বয়ানে আমরা শেষ পর্যন্ত হাজির হই বাঙালি জাতীয়তাবাদে। আমাদের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতাকে পরিষ্কার করে না। তার ভাষাভঙ্গির মোহনীয়তায় কোনো ক্রিটিক্যাল জায়গার বদলে বাংলাদেশ প্লাবিত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জনপ্রিয় ধারণাগুলোই জাদুময়ভাবে প্রাণ লাভ করে। তাদের দার্শনিক অসারতা ও বাগম্বড়তা এখানে পুরো মাত্রায় হাজির। এবং মুচমুচে ও সুস্বাদুভাবে।
ভাষার সঙ্গে সমাজকে বিশেষভাবে রূপায়ণের একটা বিষয় তো ঘটেই চলেছে। গ্রাম নিয়ে বলি, যেহেতু ওয়ালীউল্লাহ তিনটি উপন্যাসই গ্রাম-সম্পর্কিত। ভাষার কারণে ওয়ালীউল্লাহ্্ বা জহিরের গ্রাম আলাদা। গ্রামের ভাব-ভাষা ব্যাখ্যাত হয় শহরের তত্ত্বকথার মধ্যে। শহরের ভেতর থেকে গ্রাম নতুন প্রাণ পায়। অনেকটা গ্রাম নিয়ে বর্তমান শহরবাসীদের নস্টালজিয়ার মতো। এমনকি গ্রামের রহস্য বা অলৌকিকতা ছাঁচে বাঁধানো। তো, সেই পুরনো গ্রামের কি হলো আমাদের জানা হয় না। সত্য নামক ধারণাটি হয়তো দার্শনিক প্রপঞ্চ আকারে গোলমেলে। তবে কিন্তু আমরা যে সমাজে বসবাস করি, এইসব কল্পনা, বাদণ্ডবিবাদ যার থেকে তুলে আনি তার বাহ্যিক সত্যও এখানে গোপনই থেকে যায়। ফলে আমাদের আকাঙ্ক্ষার বীজগুলো কোথা থেকে আসে আর কোথায় যায় আমাদের জানা হয় না। খণ্ডই আমাদের কাছে অখণ্ড। তার তাৎপর্যও বৃহৎ হয়ে দীপ্যমান। সে আলোর নিচের ছায়া ঢাকা পড়ে যায়। তারপরও বিশেষ কোনো দিক থেকে এইসব কাজ তাৎপর্যমণ্ডিত। আমাদের ব্যাপ্তি, সীমাবদ্ধ, আকাঙ্ক্ষা ও আকাঙ্ক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটায়। বিশেষ সময়ের চিন্তাকে দারুণভাবে বহন করে।
হতে পারে ভাষাগতভাবে আমরা বিশেষ চিন্তা বা সমাজ বা দুনিয়া বা রাজনীতির অনুগামী হই। হতে পারে তাদের লেখা নিয়ে এইসব বলাবলির মধ্যে উল্লম্ফন আছে। এটি একটি বিশেষ মনের বিশেষ চিন্তাকে প্রকাশ করার নিমিত্তে তোলা ক’টি বাক্য বা উপকরণ মাত্র। কিন্তু সে তো স্থান-কাল থেকে চ্যুত না। সামাজিক সত্তা আকারেই তার এমন অনুমান ঘটে। নিশ্চয় এই রকম কিছু ঘটেছে বলে তার অনুমান হয়। চিন্তা আর যুক্তির বিজ্ঞানের দিক থেকে অনুমানকে খাটো করা যায় না। হয়তো এগুলো পরীক্ষার বাসনাও আমরা রাখতে পারি। নাও পারি। রাখাটা মনে হয় না রাখার চেয়ে ভালো।
………………………………………….
– ওয়ালীউল্লাহ মৃত্যুর প্রায় ৩০ বছর পর তার দুটি বই বাংলায় অনূদিত হয়েছে। বই দুটির নাম- ‘কদর্য এশীয়’ ও ‘কীভাবে সীম রান্না করতে হয়’।
– লেখাটি আলোকিত বাংলাদেশের সাপ্তাহিক আয়োজন শুক্রবার-এ প্রকাশিত।