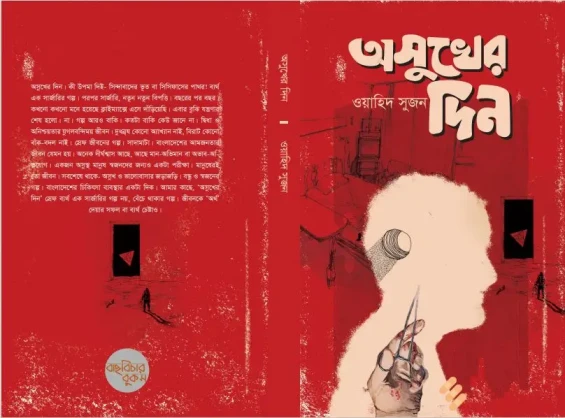তিনজন ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন। দুজনের গায়ে পুলওভার, একজনের গায়ে চাদর। মার্চের শেষ দিনে তারা শীতের দেশে যাচ্ছেন বোধহয়। আর আমার গায়ে টিশার্ট, সহযাত্রীর গায়ে ফিনফিনে শার্ট। যদিও বিকালে শিলাবৃষ্টি হয়েছে, তাই বলে এত প্রস্তুতি? এসব যখন ভাবছি— সেই তিনজন আমাদের বাসে উঠলেন। সামনে ৮-১০ ঘণ্টার জার্নি। চিন্তার বিষয়। কী বলেন?
এক.
বাসে তেমন ঠাণ্ডা লাগেনি। জানালা বন্ধ থাকায় একটা আরামদায়ক অনুভূতির মধ্য দিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জের কানসাট পৌঁছে গেলাম। মাঝে ঘুম ভাঙল দু-একবার, টাঙ্গাইলের জ্যামও তেমন কাবু করল না। হঠাৎই দেখলাম বড়সড় একটা ব্রিজ পার হচ্ছি, কেউ একজন বলল ‘মহানন্দা’। মহানন্দা! আধো ঘুমে মাথায় এল— তাকে দেখেছিলাম সেই তেঁতুলিয়া সীমান্তে। এখানে এল কী করে?
ইন্ডিয়া সীমান্তঘেঁষা কানসাটে নামলাম, তখন সকাল ৬টা বাজে। রাস্তা বৃষ্টিতে ভেজা। নিঃশ্বাসের সাথে বুকের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে সে ঘ্রাণ। ঠাণ্ডা লাগছে বেশ! ব্যাকপ্যাক থেকে শার্ট বের করে টিশার্টের ওপর চাপিয়ে নিলাম। মেঘে মেঘে ধূসর আকাশে খেলা করছে ঝাঁক ঝাঁক কাক। উন্নয়নশীল দেশের বৈদ্যুতিক তার এগুলোর খেলাঘর।
পরিকল্পনা এমনই— আমরা প্রথমে সোনামসজিদ স্থলবন্দর যাব। পুরাকীর্তি দেখতে দেখতে সোনামসজিদ হয়ে আবার কানসাট। কাছের একটা হোটেলে পরোটা-ডাল-ডিম খেয়ে গাড়ির খোঁজে বের হলাম।
ঘড়ির কাঁটা বলতে পারে সূর্য উঠেছে কিনা। রাস্তার এক ভাগ ভাঙা, গড়াগড়ি খাচ্ছে কাদা-পানি। অন্য পাশ সদ্য ঢালাই করা। সে অংশ দিয়ে এগোচ্ছি। পথে কয়েকজনকে দেখলাম ভ্যানে করে ঘাস বিক্রি করছে। এক মুঠি ৪ টাকা, ছাগলের খাবার। ঘাসও বিক্রি হয় জানতাম না। ভাবতাম ছড়াকারের কল্পনা, ‘ঘাস কী হবে? বেচবো হাটে।’
একটা অটো পাওয়া গেল। বসলাম চালকের পাশে। যাত্রীরা সোয়েটার পরা। জিজ্ঞাসা করলাম, এ অঞ্চলের শীত-গরম দুটোই কি বেশি? চালক বললেন, ‘আছে এক রকম। গরম ৪০ ডিগ্রি পর্যন্ত ওঠে। দুই-একদিন ৪২ ডিগ্রিও ওঠে।’ এমনভাবে বলছেন, মনে হচ্ছে ৪০ ডিগ্রি কোনো ব্যাপারই না। এদিকে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। রীতিমতো কাঁপছি!
দুই পাশে সারি সারি আম বাগান। কোনো গাছে মুকুল, আবার কোনোটায় নেই। গতরাতের শিলাবৃষ্টির কীর্তি। যদিও তারা বলছেন পাথর বৃষ্টি। খানিকটা পর বুঝতে পারলাম শিলা মানে পাথর হতে পারে, বরফ তো নয়ই। কয়েক কিলোমিটার যেতেই হাতের ডানে পড়ল সোনামসজিদ। তার দুই কিলোমিটার পর স্থলবন্দর।
৮টাও বাজেনি। স্থলবন্দরের সংরক্ষিত এলাকায় কয়েকজন বিজিবি জওয়ানকে দেখা গেল। আমাদের কাছাকাছি ঘুরঘুর করছে এক কিশোর। সে জানাল, আরেকটু বেলা বাড়লে বন্দর খুলবে। এখান থেকে পুরনো একটা দেয়াল আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। মন্দির, ইন্ডিয়ায় পড়েছে। কথায় কথায় এতটুকুন ছেলে জানাল, সোনামসজিদের খাদেম সে। তার কাছ থেকে কিছু তথ্য পাওয়া গেল আশপাশের।
তার দেখানো কনটেইনার ডিপোর দেয়ালঘেঁষে যাওয়া পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নির্দেশনা চোখে পড়ে। সামনে থানিয়াদীঘি মসজিদ। আম বাগানের ভেতর পথ। এরই মাঝে বিশাল এক দীঘি, থানিয়া দীঘি বা খঞ্জন দীঘি। এ ধরনের আম বাগানে প্রথমবার আসা। বিশাল বিশাল গাছ। মাটি থেকে অল্প উপরেই মোটা মোটা ডাল ছড়িয়ে উঠেছে। হাত বাড়ালে মুকুল বা ছোট আম। আগের রাতের তাণ্ডবে কোনো কোনো ডাল শূন্য। তার মাঝে দেয়ালঘেরা সুন্দর মসজিদটি।

সামনে থানিয়াদীঘি মসজিদ। আম বাগানের ভেতর পথ। এরই মাঝে বিশাল এক দীঘি, থানিয়া দীঘি বা খঞ্জন দীঘি।
উজ্জ্বল মেটেরঙা এ মসজিদের চারটি গম্বুজ, এর মধ্যে একটি প্রধান। একে চামচিকা, রাজবিবি মসজিদসহ আরো কী কী নামে যেন ডাকা হয়। মসজিদটি ইটের তৈরি, দেয়ালে নানা ধরনের কারুকাজ।
উজ্জ্বল মেটেরঙা এ মসজিদের চারটি গম্বুজ, এর মধ্যে একটি প্রধান। একে চামচিকা, রাজবিবি মসজিদসহ আরো কী কী নামে যেন ডাকা হয়। মসজিদটি ইটের তৈরি, দেয়ালে নানা ধরনের কারুকাজ। বাইরে চারদিকে রয়েছে পানি নিষ্কাশনের নালা। উপরের স্লাবগুলোয় ছোট ছোট ছিদ্র, যাতে নালার ভেতর পানি প্রবেশ করতে পারে! কত আগের কীর্তি? ১৪৫০ থেকে ১৫৬৫ সাল অবধি গৌড় ছিল বাংলার রাজধানী; এ সময়ই মসজিদটি নির্মিত হয়।
এলাকাটি মধ্যযুগের অন্যতম বৃহৎ নগরী গৌড়ের অন্তর্গত। পাল আমল থেকে শুরু করে সুলতানি ও মোগল আমলে অঞ্চলটি গুরুত্ব পেয়েছে। তার কীর্তি ছড়িয়ে আছে বর্তমান বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ভারতের মুর্শিদাবাদ ও মালদাজুড়ে। বিখ্যাত কিছু স্থাপনা পড়েছে ভারতীয় অংশে।
মসজিদের সামনে একটি টি স্টল। সেখানে পাওয়া গেল চাবি। তালা খুলে ঘুটঘুটে অন্ধকার মসজিদে ঢুকে দেখা গেল বিদ্যুৎ নেই। একটা দেয়ালের পুরুত্ব দুই হাতের বেশি। ডান পাশের একটা দরজা খুলে দিতেই আবছা আলোয় দেখতে পেলাম ভেতরটা। শত শত বছরের ইতিহাস বুকে নিয়ে চুপ হয়ে আছে। কত প্রার্থনা, চাওয়া-পাওয়ার সাক্ষী এটি। কেউ হয়তো রাতভর ইবাদত করেছেন, কেঁদেছেন, স্রষ্টাকে ডেকেছেন, দেখতে চেয়েছেন, ফানা-বাকায় যেতে চেয়েছেন।
এখন সেসব নেই। শুধু পাঁচ ওয়াক্তে পাঁচবার দরজা খোলা হয়। আর বাকিটা সময়, যখন কেউ থাকে না, তখন কি কিছুই থাকে না? না থাকার ভেতর কি ‘থাকা’ উদ্ভাসিত হয় না! তা জানা হয় না। কিন্তু প্রাচীনত্ব আর গাম্ভীর্যের একটা সুর টের পাওয়া যায়, যার সামনে এখনকার নির্মাণ ফিকে হয়ে আসে।
মসজিদের দরজা লাগিয়ে দীঘি লাগোয়া আরেকটি টি স্টলের সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসে চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করি, আশপাশে আর মসজিদ আছে? দোকানি বললেন, ‘বাগান ধরে সোজা এগিয়ে গেলে পড়বে ধানিয়াচক মসজিদ।’ কিছুক্ষণ আগে আম বাগানের গল্প করছিলাম। বলছিলাম কত বড় বাগান, আর কত বড় বড় গাছ। এবার তো বাগান শেষ হতেই চায় না। আমার সফরসঙ্গীর বাড়ি মেহেরপুরে। তার কাছে আগে আম বাগানের গল্প শুনেছিলাম। এখন শুনলাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জের একটা আম বাগানের ভেতরে পুরো মেহেরপুর এটে যাবে!
একটা ঘাসে ছাওয়া ঢিবির ওপর ধানিয়াচক মসজিদ। বেশ খোলামেলা জায়গা। রোদে মসজিদ ঝিকঝিক করছিল। ইট আর নকশার সরল বিন্যাসে নির্মিত। দরজায় তালা। আশপাশে কোনো দোকানপাট বা মানুষই দেখা গেল না। প্রাচীন কীর্তি আকারে একটা রেনোভেশন হয়েছে, নইলে এখানে মসজিদের কথা ভাবা যায় না। সামনে একটা পুকুর। মসজিদের চারপাশের মাটি ফুঁড়ে দেখা যাচ্ছে পুরনো কবরের অবয়ব। এ ধরনের সমাধি আগে দেখিনি। এখানে ও পরে সোনামসজিদ, সৈয়দ শাহ নেয়ামত উল্লাহর মাজারে দেখেছি। কোথায় যেন শুনেছি এ পদ্ধতিতে শিয়ারা কবর সংরক্ষণ করে।
বাগানঘেরা নির্জন এলাকায় মসজিদ, নিশ্চয়ই পাঁচবেলা খুব কমই লোক হয়। আমাদের কথাবার্তায়ও ভঙ্গ হলো না নির্জনতা। আরো যেন চেপে বসে। আবার ফিরতি পথ ধরলাম। পথে দুজন লোকের সঙ্গে দেখা হলো। তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, অন্য কোনো পথ আছে? এক নারী বললেন, ‘এদিকে একটা রাস্তা আছে, চুকা হবে।’ বাহ! নতুন শব্দ। শুনতে ভালোই লাগল। তার নির্দেশনা মতে পথ ধরে সোনামসজিদে ফিরে এলাম।
পথ! এসব পুরনো দিন কেমন যেন অস্বস্তি জাগায়। এই যে পথ ধরে ধানিয়াচকে এলাম-গেলাম, এটা নিশ্চয়ই প্রাচীন সেই পথ নয়, যা ধরে সেকালের মুসল্লিরা আসা-যাওয়া করতেন।
এ ধরনের আরো লেখা ইচ্ছেশূন্য মানুষ । ভ্রমণ
প্রাচীন পথগুলো সবসময় যেন নিজেকে আড়াল করতে চায়, যাতে চিহ্ন ধরে পৌঁছতে না পারি অতীতে। কেন এই লুকোচুরি? অথচ ঠিক ঠিকই আমরা ফিরে আসি চিহ্নের কাছে। আরো বেশি আপন করে পেতে চাই। আর যা আড়াল থাকে, তা যদি চোখের সামনে এসে দাঁড়াত, তবে নতুন নতুন অর্থ ও ভাবনা খেলত। কখনো কি সময়ের এ ফারাক এক হওয়ার নয়?

একটা ঘাসে ছাওয়া ঢিবির ওপর ধানিয়াচক মসজিদ। বেশ খোলামেলা জায়গা। রোদে মসজিদ ঝিকঝিক করছিল। ইট আর নকশার সরল বিন্যাসে নির্মিত।
দুই.
বিশাল একটা এলাকা ঘিরে ছোট সোনামসজিদ। ফটকের বাইরে অনেকগুলো প্রাচীন কবর। কাদের কবর, তা জানা যায় না।
সোনামসজিদকে নাকি বলা হতো গৌড়ের রত্ন। মসজিদটির বাইরের দিকে সোনালি রঙের আস্তরণ ছিল, সূর্যের আলো পড়লে নাকি সোনার মতো ঝলমল করত। তাই সোনামসজিদ নামটি দেন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব জরিপের (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া) প্রতিষ্ঠাতা স্যার লর্ড ক্যানিংহাম।
সুলতান আলাউদ্দিন শাহর রাজত্বকালে (১৪৯৩-১৫১৯) মনসুর ওয়ালি মোহাম্মদ বিন আলি মসজিদটি নির্মাণ করেন। সোনার মতো ঝলমল করে— বিষয়টি ইন্টারনেটে পাওয়া। আমরা সেই মেঘলা দিনে দেখি মসজিদের বাহির-ভেতরের আস্তরণ তো ধূসর পাথরে তৈরি। আমাদের মনে হলো, এ কারণটা স্থানীয় অন্যান্য স্থাপত্য থেকে আলাদা করেছে।
বর্ণনা পাওয়া এভাবে। দেয়ালগুলো ইটের কিন্তু মসজিদের ভেতর ও বাহির পাথর দিয়ে ঢাকা। তবে ভেতরের দেয়ালে যেখানে খিলানের কাজ শুরু হয়েছে, সেখানে পাথরের কাজ শেষ হয়েছে। মসজিদের খিলান ও গম্বুজ ইটের তৈরি। মসজিদের চার কোণে চারটি বুরুজ আছে। এগুলোর ভূমি নকশা অষ্টকোণাকার। বুরুজগুলোয় ধাপে ধাপে বলয়ের কাজ আছে। বুরুজগুলোর উচ্চতা ছাদের কার্নিশ পর্যন্ত।
এ মসজিদে নারীরা হরদম ঢুকছে, বেরোচ্ছে। মানতের উসিলায় আসছেন অনেকে। ছবি তুলতে গিয়ে অস্বস্তি হচ্ছিল। খাদেমদের অবশ্য এসব বিষয়ে আপত্তি দেখা গেল না।
ভেতরে বেশ ঠাণ্ডা। মসজিদের আলো-আঁধারির ভেতর আমরা অনেকক্ষণ বসে রইলাম। বাইরে থেকে আসা আলোয় নানা ধরনের ছায়া খেলছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। আমরা নামাজ পড়লাম।
এখানকার পুরনো মসজিদের অনেকগুলো প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তর রিইনোভেশন। তাদের অধীনে অনেক মসজিদ সংরক্ষিত হলেও নানাভাবে ভেতরের সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে বৈদ্যুতিক তার ও পাখার যত্রতত্র ঝুলে থাকা মূল কাঠামোকে নষ্ট করছে। সোনামসজিদও ব্যতিক্রম নয়। প্রার্থনা গৃহ হলেও এগুলোর ঐতিহ্যগত ও স্থাপত্য মূল্য কম নয়।
মসজিদের বাইরে খোলা প্রাঙ্গণে আছে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের সমাধি। সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা মেজর নাজমুল হকের সমাধি। কবরে সালাম জানিয়ে বের হয়ে আসি প্রধান ফটক দিয়ে। আকাশে তখন পুরোপুরি রোদ হাসছে।

তাহাখানা কমপ্লেক্স। কানসাটের বাকি স্থাপনাগুলো সুলতানি আমলের হলেও তাহাখানা নির্মাণ করেছেন মোগল শাহজাদা সুজা।
এরপর কোথায় যাব? তাহাখানা কমপ্লেক্স। কানসাটের বাকি স্থাপনাগুলো সুলতানি আমলের হলেও তাহাখানা নির্মাণ করেছেন মোগল শাহজাদা সুজা। শাহজাহানের এ ছেলে ২০ বছর বাংলার সুবাদার ছিলেন। তিনি ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করেন। তবে সুবাজুড়ে তার নানা কীর্তি এখনো চোখে পড়ে।
শাহ সুজা তার গুরু সৈয়দ শাহ নেয়ামত উল্লাহর উদ্দেশে শীতকালীন বসবাসের জন্য তাপনিয়ন্ত্রণ ইমারত হিসেবে তাহাখানা নির্মাণ করেন ১৬৫৫ সালে। তাহাখানা ফার্সি শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ ঠাণ্ডা ভবন। মাঝে মাঝে শাহ সুজাও এখানে বাস করতেন। আর যে স্থানটি নেয়ামত উল্লাহর খানকা ছিল, তা এখন মাজার।
এটি মূলত একতলা ভবন, একটা খোলামেলা বেসমেন্ট আছে, যার মুখেই পুকুর। দুটি অষ্টকোণ আকৃতির কক্ষসহ ১৭টি কক্ষ আছে উপরতলায়। নামাজ ঘর, ভোজন কক্ষ, ক্ষৌরকর্ম কক্ষ, বিশ্রামাগার আছে। আছে হাম্মামখানাও। হাম্মামখানা ও প্রসাধনাগারে মাটির পাইপের জন্য ঠাণ্ডা ও গরম পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। আর পুরো ভবনটি চুন-সুরকি সাহায্যে ছোট আকারের ইটে তৈরি।
শাহ নেয়ামত উল্লাহর মাজার যা এক সময় খানকা ছিল, তার সামনে বোর্ডে লেখা আছে জন্ম ১৫৬৫ থেকে ৭০ সালের ভেতর, আর মৃত্যু ১৬৬৪ থেকে ৭০ সালের ভেতর। অবশ্য ১৬৬০ সাল পর্যন্ত সুবাদারের দায়িত্ব পালন করেন শাহ সুজা। এর আগে থেকেই সিংহাসন দখলে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন তিনি। ওই বছরই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আরাকান পালিয়ে যান। পরে আরাকান রাজার বিশ্বাসঘাতকতায় সপরিবারে নিহত হন। এর কারণ নিয়ে নানা ধরনের মত রয়েছে।

কোরাইশ বংশীয় নেয়ামত উল্লাহর পর দাদারা আরব থেকে আসেন। তার জন্ম দিল্লি অথবা কাশ্মীরে। শুধু শাহ সুজা নন, বাবা শাহজাহান ও ভাই আওরঙ্গজেবও ছিলেন তার ভক্ত।
কোরাইশ বংশীয় নেয়ামত উল্লাহর পর দাদারা আরব থেকে আসেন। তার জন্ম দিল্লি অথবা কাশ্মীরে। শুধু শাহ সুজা নন, বাবা শাহজাহান ও ভাই আওরঙ্গজেবও ছিলেন তার ভক্ত। কথিত আছে, নেয়ামত উল্লাহকে পরীক্ষার জন্য এক গ্লাস বিষাক্ত পানি পান করতে দেন শাহ সুজা। তিনি অর্ধেক পান করে বাকিটা পুকুরে ছুড়ে দিলে দাফিউল বালায় (বিপদ প্রতিরোধক) পরিণত হয়। পুকুরের নাম হয়ে যায় তালাবে শেফা। বোর্ডে যখন এসব পড়ছিলাম নেয়ামত উল্লাহর মাজার থেকে এক বয়স্ক ভদ্রলোক বের হয়ে এলেন, মাথায় সবুজ টুপি। এক সঙ্গীসহ সোনামসজিদেও দেখেছিলাম তাকে। তিনি তালাবে শেফার গুণাগুণ বর্ণনা করছিলেন।
বলা হচ্ছে, আরবিতে যতটা অক্ষরে আছে, ঠিক ততটা অক্ষরে ফারসিতে কোরআনে অনুবাদ করেছিলেন নেয়ামত উল্লাহ। শাহজাহান ৪০০ বিঘা ও আওরঙ্গজেব তাকে দেন ২ হাজার ৯২১ একর জমি। অদ্ভুতই লাগে— আওরঙ্গজেবের কারণে শাহ সুজার জীবনে যত বিপত্তি, আর শাহজাহান বন্দি জীবন যাপন করেন।
মোগল শাসনে উত্তরাধিকার নির্বাচিত হতো তলোয়ারের শক্তি দ্বারা। নেয়ামত উল্লাহ কি ভক্তদের মধ্যকার এ বিরোধের মীমাংসার চেষ্টা করেননি। কেউ কেউ তো ঠাট্টা করে বলেন, কোনো মোগল সম্রাট নাকি হজ করেননি, পাছে যদি ক্ষমতা দখল হয়ে যায়।
আরো জানা গেল, ১ মহররম শাহ নেয়ামত উল্লাহর জন্ম ও মৃত্যুদিনে ওরশ হয়। ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার তার আগমন উপলক্ষে ওরশ অনুষ্ঠিত হয়।
ইন্টারনেটে নেয়ামত উল্লাহ-সম্পর্কিত তথ্য খুঁজতে গিয়ে আরেকজনের সন্ধান পেলাম। তার নাম শাহ নেয়ামাত উল্লাহ ওয়ালী (রহ.)। তিনি কাব্য বা কাসিদার জন্য বিখ্যাত। এতে দুনিয়ার নানা ঘটনাপরম্পরা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। ‘গাজওয়াতুল হিন্দ’ নামের হাদিসে আছে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম ও মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধের কথা, যাতে মুসলিমরা জয় লাভ করবে। তাও উল্লেখ আছে এ কাব্যে।
বলা হয়ে থাকে, ১১৫২ সালে ইলহামের জ্ঞান দ্বারা শাহ নেয়ামত উল্লাহ বিখ্যাত কাব্যগুলো রচনা করেন। ব্রিটিশ বড় লাট লর্ড কার্জনের শাসনামলে এর প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। খুবই কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার। আপাতত এ নিয়ে ভাবার তেমন সুযোগ নাই। শুধু শেষ কাব্যটি উল্লেখ করছি— ‘চুপ হয়ে যাও ওহে নেয়ামত। এগিয়ো না মোটে আর। ফাঁস করিও না খোদার গায়েবি রহস্য।’
তাহাখানার পাশেও আম বাগান, সাথে সরকারি স্কুল। স্কুলে খেলাধুলা হচ্ছে। অনেককে দেখা গেল উকিঝুঁকি মারতে। বিক্রি হচ্ছে আচার, শরবত, বাদাম, সরিষা মাখানো পেয়ারাসহ অনেক কিছু। আমরা পেয়ারা নিলাম। খেতে খেতে এক ভ্যানওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোতায়ালি দরজা যাবেন? উনি জানালেন, এ নামে তিনি কিছু চেনেন না, তবে দারাস মসজিদ আর মাদ্রাসা চেনেন। বললাম, চলেন ওইখানে? পরে জেনেছিলাম, কোতোয়ালি দরজা ভারতে পড়েছে।
আবার স্থলবন্দরের দিকের রাস্তা ধরে চলছি। এরপর পাথরের ডিপোর ভেতর দিয়ে পড়লাম কাদাময় এক রাস্তায়। সেই রাস্তার পাশে কড়া রোদে স্বর্ণের মতো ঝিকমিক করছে গমের শীষ! তারপর আম বাগানের পাশের রাস্তা ধরে মুখোমুখি হলাম দারাস মসজিদের। দেখে জবান বন্ধ হয়ে এল।

দারাসবাড়ি মসজিদ। সাত দরজার বিশাল দালান। ধ্বংসাবয়ব দেখে বোঝা যায় সামনে সাতটি পিলার ছিল। কী তার গাম্ভীর্য, কী তার রূপ! কেন জানি মসজিদ মনে হচ্ছিল না। ইট আর টেরাকোটার দালানটার ওপর কোনো ছাদ নেই, মানে বিলীন হয়ে গেছে।
তিন.
সাত দরজার বিশাল দালান। ধ্বংসাবয়ব দেখে বোঝা যায় সামনে সাতটি পিলার ছিল। কী তার গাম্ভীর্য, কী তার রূপ! কেন জানি মসজিদ মনে হচ্ছিল না। ইট আর টেরাকোটার দালানটার ওপর কোনো ছাদ নেই, মানে বিলীন হয়ে গেছে। সময় তার মাথার ওপর খুলে দিয়েছে অসীম আকাশ। স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে সমগ্রতা, বিশালতা। ভাবছিলাম যা আছে তা-ই যথেষ্ট, নতুন করে গড়তে গেলে পুরনো যতটুকু স্মারক, তাও থাকবে না হয়তো।
দালানের এক পাশে তিনটি দরজা, উল্টোদিকে দুটি। আর ওই দুটি দরজার মাঝে কুণ্ডলীর মতো কিছু একটা। দেখে ফায়ারপ্লেস মনে হচ্ছিল। ওই সম্ভবত আরেকটা তলা ছিল, যেখানে নারীরা নামাজ পড়তেন। মোট তিনটা কামরা। মাঝের দুই দেয়ালে তিনটি তিনটি দরজা। দোতলা সমান উঁচু। ইমাম সাহেবের দাঁড়ানোর জায়গা দেখা গেল। আগে দেখা অন্যান্য মসজিদের মতো এখানেও মিম্বার নেই। থাকলেও কালের গর্ভে ঠাঁই নিয়েছে তা।
ইন্টারনেট ঘেঁটে জানা গেল বেশকিছু তথ্য। মুনশি এলাহি বখশের আবিষ্কৃত একটি আরবি শিলালিপি অনুযায়ী ১৪৭৯ সালে সুলতান শামস উদ্দীন ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে তারই আদেশক্রমে মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন নাম দারাসবাড়ি ছিল না, ছিল ফিরোজপুর জামে মসজিদ। ১৫০২ সালে সুলতান হোসেন শাহ দারাসবাড়ি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করলে অঞ্চলটির পরিচিতি পায় দারাসবাড়ি নাম। আর হ্যাঁ, দর্স অর্থ পাঠ।
দীর্ঘদিন মাটিচাপা পড়েছিল এ মসজিদ। সত্তর দশকের প্রথম ভাগে খনন করে উদ্ধার করা হয়। মসজিদের সামনে বিশাল পুকুর বা দীঘি, তার অন্যপাড়ে দারাস মাদ্রাসা। এখানে কিছু অবকাঠামোর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। বুক সমান উঁচু দেয়াল।
মাদ্রাসার সামনে থাকা নোটিস বোর্ডে জানা যায়, বর্গাকার চত্বরের পশ্চিম বাহু ব্যতীত অন্য বাহুতে এক সারি করে প্রকোষ্ঠ এবং তিন বাহুর মধ্যবর্তী একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। পশ্চিম বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে পাশাপাশি তিনটি সালাতকোঠা রয়েছে। সালাতকোঠার পশ্চিম দেয়ালে তিনটি অবতল মেহরাব রয়েছে। শোভাবর্ধক পোড়া মাটির ফলক ও নকশা করা ইট দিয়ে দেয়ালগুলো অলঙ্কৃত।
সম্ভবত এটিই বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন মাদ্রাসার নির্দশন। ১৯৭৩ সালে স্থানীয় লোকজন চাষাবাদের সময়ে কালো পাথরের একটি শিলাঢিবি আবিষ্কৃত হয়। পরে ১৯৭৫ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালনা করা হয়।
সত্যি বলতে কী দারাসবাড়ি মসজিদ এতটাই অভিভূত করে যে, আমরা তেমন কিছু ভাবতেই পারছিলাম না। কখনো দেয়াল, কখনো বা থাম স্রেফ দেখছিলাম, কখনো বা স্রেফ আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কোনো কারণ ছিল না, দেখাদেখি শেষ হতে বেশিক্ষণ লাগেনি। কিন্তু কেন যেন আমাদের দেখা শেষ হচ্ছিল না। এদিক ওদিক ঘুরছিলাম শুধু। পরে মনে হলো সবশেষে দারাসবাড়ি মসজিদ দেখে একটা সুন্দর সমাপ্তি হলো ভ্রমণের।

দারাসবাড়ি মাদ্রাসা। এটিই বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন মাদ্রাসার নির্দশন। ১৯৭৩ সালে স্থানীয় লোকজন চাষাবাদের সময়ে কালো পাথরের একটি শিলাঢিবি আবিষ্কৃত হয়। পরে ১৯৭৫ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালনা করা হয়।
চার.
যখনই এমন স্থাপনার সামনে দাঁড়িয়েছি, স্পর্শ করেছি— অদ্ভুতভাবে নিজেকে তুচ্ছ মনে হয়। শুধু এ কারণে নয় যে, এসব জড় নির্মাণের কাছে নিজেকে সীমিত মনে হয়েছে। হয়তো এর সত্তাগত মূল্য নেই। বা থাকলেও আমি অনুধাবন করতে পারি না। আমরা শুধু এর সৌন্দর্যগত মূল্য দিয়ে থাকি। কিন্তু কালের সাক্ষী হিসেবে এগুলোর মূল্য সীমায়িত করতে পারি না। বা প্রাচীনতার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার বিষয়টা অবহেলা করতে পারি না।
সাক্ষী কিসের? অতীত। অতীত তো বহমান এক স্রোত! প্রশ্ন তুলতে তুলতে কিছু সময় তার হাতে তুলে দিই। দেখা হয় হয়, আবার হয় না যেন। অনেক বছর আগে— ষাট গম্ভুজ মসজিদের ঠাণ্ডা থাম স্পর্শ করেছিলাম। আমি যেন স্থির হয়ে গেলাম। দেখতে পাচ্ছিলাম কত কত সময় বয়ে যাচ্ছে, কত মানুষ-কোলাহল দূরে দূরে সরে যাচ্ছে। আবার উয়ারি-বটেশ্বর ধরে হাঁটলে পায়ের নিচের প্রাচীন রাস্তা কি আনমনা করে না? মনে কি হয় না— কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলাম। মুখোমুখি হলাম পুরনো দিন, পুরনো মানুষের। আমরা তো প্রাচীনতার খোঁজ করছি মানুষের মুখোমুখি হতে। মানুষ ছাড়া তো মনের কথা বলা যায় না। কিন্তু অতীত আর বর্তমানের ফানা হয় না। হায়! কিছুই স্থির নয় এ চরাচরে।
এই যে সাক্ষী বলছি। অথচ এগুলো এক সময় ধ্বংস হয়ে যায়। এসবের কিছু কিছু আমরা আবার তৈরি করি। তবুও এটা একদম নতুন গল্প। পুরনো গল্প নানা ‘সম্ভাবনা’র ভেতর দিয়ে নতুন করে রচিত হয়। এভাবে কি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে অচ্ছেদ্য হয়ে পড়ি। এ ভাবনার ভেতরেই বোধহয় অতীত ও বর্তমানের ফানা হয়। তবে কি গৌড়ে সবই বর্তমান? জানি না। ভাবলে মন কেমন করে!

হঠাৎই দেখলাম বড়সড় একটা ব্রিজ পার হচ্ছি, কেউ একজন বলল ‘মহানন্দা’। মহানন্দা! আধো ঘুমে মাথায় এল— তাকে দেখেছিলাম সেই তেঁতুলিয়া সীমান্তে। এখানে এল কী করে?
দুপুরে খাইনি। এটা জানতেন ভ্যানচালক ভাই। তিনি সোনামসজিদে নিয়ে এলেন। এখানে পাশাপাশি দুটি হোটেল— সোনারগাঁও, শেরাটন। কোনো একটাতে খেলাম। তারপর কানসাট হয়ে ফিরে এলাম মহানন্দা ব্রিজে। মাঝে একটা ধারা বয়ে যাচ্ছে এই নদীর। এক পাশে চরে ধানক্ষেত। উপর থেকে যখন দেখছিলাম— সবুজ জ্যামিতিক নকশা কাছে ডাকছিল যেন। সন্ধ্যাতক বসে রইলাম সবুজ ঘাসে। সামনে বয়ে যায় নদী। সময়ের মতো। আর হ্যাঁ, আমাদের ভ্রমণ বেশ ভালো ভালোই শেষ হয়। রাতের খাবারের মেনুতে ছিল নিমতলার কলাই রুটি ও গরুর মাংস। সে স্বাদ নিয়ে ফিরলাম ঢাকায়।
: লেখাটি বণিক বার্তার সাপ্তাহিক আয়োজন সিল্করুটে প্রকাশিত।