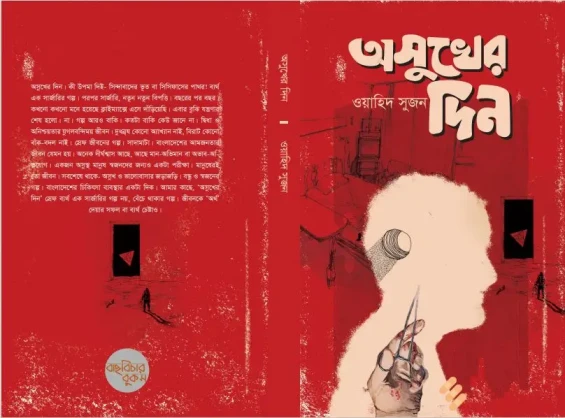এক.
এনজিওর নাম ‘জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদ’। মধুপুর বন দেখতে গিয়ে উঠেছিলাম ওখানে। নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে, প্রতিষ্ঠানটি আদিবাসীদের নিয়ে কাজ করে, আর ‘জয়েনশাহী’ শুনতে একটু অদ্ভুতই লাগল। এলাকার নাম তো নয়ই, আদিবাসী কোনো শব্দও মনে হলো না।
ঘোরাঘুরির একপর্যায়ে জয়েনশাহীর হদিস পাওয়া গেল। টাঙ্গাইলের সীমানাঘেঁষে ময়মনসিংহে রয়েছে হযরত জয়েনশাহীর মাজার। খুদে সাইনবোর্ড থেকে জানা যায়, জয়েনশাহী ১৫৩০ সালে মোগল সম্রাটের আদেশে এ অঞ্চলে আসেন। তাকে জঙ্গল পত্তনি দেয়া হয়। এখনকার জনবসতিতে তার দারুণ প্রভাব ছিল। অনেক পরে খাজনাবিষয়ক জটিলতার কারণে এ বন চলে যায় রানী ভবানীর জমিদারির অধীনে।
আরো শোনা যায়, ৩৬০ আউলিয়ার একজন জয়েনশাহী। ৩৬০ বললে যেমন নিখুঁত বৃত্ত মনে আসে, তেমনি আসে হযরত শাহজালাল (র.)-এর শিষ্যদের কাহিনী। আবার আসে কাবা শরিফের সেই ৩৬০ মূর্তির কথা, যেগুলো হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা বিজয়ের পর ধ্বংস করেন। মোটের ওপর ‘৩৬০’ গণিত, জ্যোতিষবিদ্যা বা ধর্মে গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। আর এখানেও জয়েনশাহী ফিরি। শাহজালাল (র.) ধরলে সময়ের হিসাব বড্ড গোলমেলে লাগে। জায়েনশাহীর সনটা শাহজালালের প্রায় ২০০ বছর পরের ঘটনা!
১৫৩০ সাল ধরলে সম্রাট বাবরের সময় বোঝায়। কারণ ওই বছরের ২৬ ডিসেম্বর সিংহাসনে বসেন হুমায়ুন। তাই খানিকটা গোলমেলে লাগে। সম্রাট আকবরের সময় বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর বাবরের নজর ছিল উত্তর ভারতে এবং তিনি সেখানে যুদ্ধও জয় করেন। সে হিসাবে জয়েনশাহী কার সময়ে পত্তনি নিয়েছিলেন তা স্পষ্ট নয়। এমনকি মোগল সম্রাটের আদেশে তিনি এ দেশে আসেন কিনা তাও স্পষ্ট নয়।
জয়েনশাহীকে নিয়ে খুব বেশি গল্প শোনার সুযোগ ঘটেনি। যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তারা এর বেশি জানেনও না। আরেকজনের নাম খুবই শুনেছিলাম।
তিনি ফাদার ইউজিন হোমরিক। আমেরিকান এ ধর্ম প্রচারক জীবনের বেশির ভাগ সময় এ মধুপুর অঞ্চলে কাটিয়ে সম্প্রতি ফিরে গেছেন স্বদেশে। জঙ্গিবাদ বা এ নামে চলা অরাজকতাই তার বাংলাদেশ ত্যাগের কারণ। এখানকার স্থানীয় মান্দিদের জীবনমান উন্নয়নে তার ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। অবশ্য সভ্যতার আলো হিসেবে এসেছে ধর্ম। ফাদারের কল্যাণে তারা ধর্মীয় পরিচয়ে খ্রিস্টান, আর সংস্কৃতিতে মান্দি। এনজিওর নোটিস বোর্ডে একটা বিয়ের কার্ড দেখলাম। কার্ডে পাত্র-পাত্রী ও তাদের মা-বাবার মান্দি নাম দেখলাম। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মার্থা, ফ্রান্সিস, পিটার, গ্যাব্রিয়েল বা এ-জাতীয় কিছু শব্দ। আরো উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, মান্দি ঐতিহ্য ধারণ করে কার্ডে বাবার আগে মায়ের নাম লেখা। মাতৃতান্ত্রিকতা আজো বহমান এখানে।
দুই.
কার্তিক-অগ্রহায়ণের দিকেই মধুপুর জঙ্গলে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। নানা ঝামেলায় সময় মিলছিল না। মাঝে চলে গেল শীত। ফাল্গুন এসে পিছলে যাওয়ার আগে খপ করে ধরে ফেলি।
এ জঙ্গলের নাম শুনেছি অনেক আগে; ইকোপার্ক বিষয়ক বিতর্কের কারণে। সেখানকার আদিবাসীদের সঙ্গে বন বিভাগের ঝামেলা আছে বিস্তর।
মধুপুর টাঙ্গাইলের একদম সীমান্তে। তার পরই ময়মনসিংহ। এখানে এসে দেখা গেল, কয়েক ফুটের দূরত্বে দুটি ফলক। একটায় লেখা টাঙ্গাইল বন বিভাগ, অন্যটিতে ময়মনসিংহ বন বিভাগ। দুটো অফিস রাস্তার এপার আর ওপার।
ময়মনসিংহ সীমান্ত পার হতেই শুরু মধুপুরের রসুলপুর। এ অঞ্চলে ঢুকতেই অরণ্য। পাতা ঝরে গেলেও পথের দুই পাশ যথেষ্ট সবুজ। গাড়ি বেশ দ্রুত এগোচ্ছিল। রোমাঞ্চ জাগাতে জাগাতেই অরণ্য হারিয়ে গেল হঠাৎ শুরু হওয়ার মতো করে। আর এল না!
এখানে কিছু তথ্য যোগ করি ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন ও চট্টগ্রামের পাহাড়ি বনাঞ্চলের পর দেশের তৃতীয় বৃহত্তম প্রাকৃতিক বন এই মধুপুর। এ বন বিশাল এক বনজ অঞ্চলের অংশ ঘিরে। টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও জামালপুর জেলায় বিস্তৃত মধুপুর বনের প্রকৃত আয়তন ৪৫ হাজার ৬৫৬ একর। ১৯৫৪ সালে সরকার এই ভূমিকে মধুপুর বনের অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯৮২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি মধুপুর বনের প্রায় ২০ হাজার ৮৪০ একর (৮৪৩৬ দশমিক ১৩ হেক্টর) জমি নিয়ে দেশের প্রথম জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয়। পরে ২০১৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অরণখোলা ইউনিয়নের ৯১৪৫ দশমিক শূন্য ৭ একর জমিকে ‘সংরক্ষিত বনভূমি’ ঘোষণা করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়। তবে বর্তমানে প্রকৃতপক্ষে চার থেকে সাড়ে চার হাজার একর জমিতে প্রাকৃতিক বনাঞ্চল রয়েছে।
বাকিটা কোথায় গেল?
তিন.
পৌঁছতে পৌঁছতে দুপুর। ফ্রেশ হয়ে খাওয়াদাওয়া মিলিয়ে বিকাল। এরপর একটা মসৃণ রাস্তা ধরে ঘুরতে বের হলাম। যেখানে একটা সিল্ক কারখানা আছে। কাপড়চোপড়ের দাম ঢাকার মতোই মনে হলো। আছে সাজানো-গোছানো গির্জা, হাসপাতাল ও বিদ্যালয়। একদম ছবির মতো, ঝকঝকে তকতকে। কোথাও কুটোটি পড়ে নেই। আদিবাসী বাড়িগুলোও বেশ সুন্দর। মাঝে একটা মক্তব দেখলাম। একদম সনাতনী ধরনের।
আদিবাসীদের গ্রাম ধরে এগোতে এগোতে চলে এলাম আনারস বাগানে। আনারসের সারির মাঝে মাঝে ইউক্যালিপটাস বা আকাশমনি উঠে গেছে আকাশ ফুঁড়ে। এমন বৈচিত্র্যহীন গাছ বোধহয় বাংলাদেশে আর নেই। তবুও এ বিদেশী গাছ শুধু এখানে নয়, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক বন উজাড় করে বানানো বনায়ন ও সামাজিক বনায়নের অংশ হিসেবে পাহাড়, রাস্তার পাশে, ক্ষেতে, ক্ষেতের আইলে দেখবেন। অথচ খোদ বন বিভাগের লোকেরাও এ বিদেশী গাছের নিন্দা করে। আরো হেঁয়ালি হলো আদিবাসী আর বিদেশী গাছের মিলিত বসবাসের মচ্ছব দেখে। দুটি যেন জগতের ভিন্ন ভিন্ন দিক নির্দেশ করছে। নাকি তারা গভীর কোনো ঐকতানের মধ্যে বিচ্ছিন্ন অনেক সুতো জোড়া দিয়ে যাচ্ছে; যার মধ্যে বৈপরীত্য আর মিলের বাসনা ধরাধরি করে হাঁটছে। তারা নির্দেশ করছে অন্য কিছু, যা কারোই নয় আপাত অর্থে।
পরদিন রেঞ্জ কর্মকর্তা বলছিলেন, সামাজিক বনায়নের মালিকানা স্থানীয়দেরও। তাদের অংশগ্রহণ জারি রাখার একটা টেকসই পদ্ধতি হলো দ্রুত অর্থ লাভের ব্যবস্থা করা। ইউক্যালিপটাস বা আকাশমনির রমরমা চাষাবাদের অন্যতম কারণ এটাও। অন্যদিকে শালগাছ বাড়তে অনেক সময় লাগে।
এ ধরনের আরো লেখে পেতে পড়ুন : জার্নাল । ইচ্ছেশূন্য মানুষ
মধুপুরের মাটি খুবই উর্বর। আনারস, কলা, পেঁপেসহ নানা ধরনের গাছ অল্প যত্নেই তরতর করে বেড়ে ওঠে। মধুপুরের ফলমূলের চাহিদা দেশজোড়া। ফল বাগানের সৌন্দর্যও দেখার মতো। আর ফল এ অঞ্চলের দূতিয়ালি করে, এর একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত মিলবে মধুপুর শহরে। শহরের একদম মোড়ে তিনটা বিশাল আনারস নিয়ে ভাস্কর্য। ফল মৌসুম আক্ষরিকভাবে এ অঞ্চলের বিশেষত্ব তুলে ধরে।
এসব ফলমূলকে অর্গানিক ভাবলে ভুল করবেন। এমনই বাণিজ্যিক নৈরাজ্যের চাপে বন উজাড় হচ্ছে প্রতিদিন কোনো না কোনো দিকে। আর বন্দুকের ট্রিগারটা ধরা হয়েছে আদিবাসীদের ঘাড়ে। হয় কি, স্রেফ ভ্রমণকারী হিসেবে তাকালে আনারস, ইউক্যালিপটাসের মিলিত বাগান দেখতে নতুনত্ব চোখে লাগে? কিন্তু এ বিষয়গুলো বাদ দিয়ে মধুপুরের অন্য আলাপ কোনোভাবেই যেন এগিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না।
আগেই বলেছিলাম, এ বনকে বেশ আগেই ইকোপার্ক ঘোষণা করা হয়। সেটা নিয়েই আদিবাসীদের সঙ্গে বন বিভাগের ঝামেলা শুরু। বন কর্মকর্তাও বলছিলেন ইকো পার্কের পরিকল্পনার অসামঞ্জস্যের কথা। যেমন— বনকে বিট হিসেবে দেয়াল দিয়ে ভাগ করে একাধিক ভাগে সংরক্ষণ করা। তাহলে আদিবাসী বা বনচর প্রাণীর নির্বিঘ্ন চলাচল কীভাবে সম্ভব?
ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায় যে, বনচর আদিবাসীদের বনের সঙ্গে আলাদা করা অনেকটা মূল থেকে তাদের বিচ্যুত করার মতো। সাদা চোখে অনুমান করা যায়, তারা ভূমির সঙ্গেই মানসিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিকভাবে যুক্ত। এ যুগেও। যদিও ধর্মান্তকরণ নতুন ধরনের অনুঘটক আকারে কাজ করে। নতুন প্রজন্মে সেই অর্থে অশিক্ষিত আদিবাসী চোখে পড়ে না। তাদের নতুন পরিচয় নির্মিত হয়েছে মিশনারিদের মাধ্যমে আসা খ্রিস্টান ধর্মের মাধ্যমে। এ পরিচয় আর পুরনো সংস্কৃতি মিলে তারা বেছে নিয়েছে নতুন ধরনের জীবনাচরণ। তারা শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হলেই শহরে পাড়ি জমাচ্ছে। বনের সঙ্গে আত্মিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি হচ্ছে। ব্যাপারটা এমন সরলতার সঙ্গে বুঝেছি।
বিশেষ করে বন উজাড়ের বিষয়টা অনেকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, বন মূলত সরকারের অধীনে হলেও আদিবাসীরা চাইলে নিজেদের জীবিকা হিসেবে বন পরিষ্কার করে বাগান করতে পারে। যেমন— আমরা বিশাল একটা এলাকা দেখেছি, পেঁপের বীজ লাগানো হচ্ছে। এভাবেই নাকি আদিবাসীদের হাতে আবাদি জমির পত্তন হয়। এরপর প্রভাবশালী কেউ (অবশ্য বাঙালি, রাজনৈতিক অর্থে প্রভাবশালী) সেটার মালিকানা খরিদ করে নেয়। এ হিসেবে দেখা যায়, উজাড় হওয়া বনের বড় অংশের মালিকানা গুটিকয়েক ব্যক্তির হাতে। আদিবাসীরা এখানে বন ধ্বংসের উপলক্ষ মাত্র। তাদের নামে মামলারও শেষ নেই।
বন রক্ষা নিয়ে বন বিভাগের কমিটি আছে, নানা ধরনের কর্মসূচি আছে। যেমন— আমাদের সামনেই ওই রকম কমিটির একজন সদস্য জানালেন, তাদের দখলে থাকা বনের জমির পরিমাণ সামান্য, তাও আবার কয়েক পুরুষের। কিন্তু রেঞ্জ কর্মকর্তা হেঁয়ালি করেই বলেন, কোনোভাবে স্বাধীনতার আগে এ ঘটনা ঘটেনি। কথায় কথায় জানা গেল, স্বাধীনতার পর পরই বন দখলের মহোৎসব শুরু। একবার কোনো একটা প্রজেক্টের আওতায় ‘বৃক্ষচোর’দের বন রক্ষায় দায়িত্ব দেয়া হয় দৈনিক হারে টাকার বিনিময়ে। কয়েক বছর পর সেই কাজ আর আগাইনি। মাঝে অপরাধীদের নিয়ে বন বিভাগ বৈঠক করছে এমন অভিযোগে পুলিশ হানা দেয়। শেষমেশ অনেক ‘বৃক্ষচোর’ আগের পেশায় ফিরে যায়। আচ্ছা, চুরি কি একটা পেশা হতে পারে? মানে, পেশার আইনগত সংজ্ঞা কী বলে?
ভাবুন, ঘোরাঘুরির ভেতর এত এত জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হলাম যে, ভ্রমণ কাহিনীই লেখা হলো না!
চার.
যদিও বসন্ত। তখনো মধুপুরে পাতা ঝরার দিন। সড় সড় শব্দে উড়ে পড়ছে পত্রপল্লব। আগের দিনের মসৃণ সেই রাস্তা ধরেই যাচ্ছিলাম। কয়েক কিলোমিটার যেতেই রাস্তা আর আগের মতো থাকল না। পার্বত্যাঞ্চলের মতো, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাস্তাও ক্ষত-বিক্ষত।
ইচ্ছে ছিল দোখলা থেকে রসুলপুর পর্যন্ত ট্র্যাক ধরে হাইকিংয়ের। নয় কিলোমিটার! ভাবছিলাম, পায়ের ওপর ভরসা করা যায় কিনা? এটা নিশ্চয়ই জানেন, ভ্রমণে বাড়তি শক্তি ভর করে শরীরে। কিন্তু সবার দেখানো ভয় পিছু ছাড়ছিল না। বনের সঙ্গে ভয়ের পিরিতি আছে যেন! কিছুদিন আগে নাকি এক সামরিক কর্মকর্তা স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে এসে ছিনতাইয়ের কবলে পড়েন।
শেষে একটা মোটরসাইকেলের ব্যবস্থা হলো: ২০০ টাকায় বন ঘুরে দেখাতে রাজি হলেন তিনি। তবে বনের অলিগলি ঘোরাবেন না। সোজা ট্র্যাক ধরে গাড়ি চালিয়ে শেষ সীমানা রসুলপুর।
বনের নিজস্ব ভাষা আছে। বন কথা বলে একা একা, আপনাকেও তাতে শরিক করে নিতে পারে। হয়তো একা আছেন। হুট করে মনে হবে আপনি একা নন। অথচ আশপাশে কেউ নেই। এ রকম অভিজ্ঞতা আগে হয়েছিল আমাদের। গা ছমছমে ব্যাপারটা কখনো ভোলার নয়। এবার সশব্দ ভ্রমণে সব রহস্য উবে গেল। দুই চাকায় ভর দিয়ে নৈঃশব্দ্যটুকু পেরিয়ে যাচ্ছিলাম। চোখ বন্ধ করতে মনে হলো উড়ছি আমরা। আর মনে যখন সবুজ ভর, কত গ্লানি নিমিষে হাওয়া হয়ে যায়।
ডান বা বাম কোথাও না, সোজাসুজি রসুলপুরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। দুই পাশ থেকে পেছন দিকে সরছে শালগাছ। আছে বেত, বাঁশসহ নানা জাতের গাছ। মাঝে মাঝে যে সর্বনাশী ইউক্যালিপটাস চোখে পড়ছে না, এমন না।
আগের দিন হাঁটতে হাঁটতে একটা কথা কয়েকবার শুনেছি আমার সঙ্গী হাবিব ভাইয়ের মুখে। বন বলতে যা আছে, তা হলো মলাট বা প্রচ্ছদ। এখানকার বন এমনই একটা যেন বই, যার ভেতরে কোনো পৃষ্ঠা নেই। ব্যাখ্যা করলেন এভাবে, পথ চলতে চলতে দুই পাশে বন দেখে মোহিত হবেন, যে পথে যান। কিন্তু হুট করে গভীরে যেতে গিয়ে দেখবেন, ও পাশে বন নেই। হয়ে গেছে পেঁপে, হলুদ, আনারস বা কলার বাগান অথবা খালি জমিন, আবাদ হবে হবে ভাব। এর জন্য ভেতরে যেতে হচ্ছে তা না। মোটরসাইকেল থেকে দিব্যি দেখা যাচ্ছিল মলাটের ভেতরের ন্যাড়া অংশ, কোথাও বা বাগান।
যেতে যেতে কিছু মানুষ চোখে পড়ল। তাদের পেশা বনের সঙ্গে সম্পর্কিত মনে হলো। আরো আছে বাঙালি ও আদিবাসী তরুণ এরা স্থানীয়, ঘুরতে এসেছে। পর্যটক বলতে শুধু আমরাই।
পথে হরিণ প্রজনন কেন্দ্র। সেখানে মিলবে বানর। পোষা। বিস্কুট বা অন্য খাবার দিলে হাত থেকে নিয়ে দিব্যি খায়। পাশে দাঁড়িয়ে বা বসে ছবি তুলতে পারেন। বিশাল এলাকা নিয়ে হরিণের খাঁচা। দূর থেকে দু-একটা হরিণ দেখলাম, আমরা যেতেই মিলিয়ে গেল। এখান থেকে হরিণ চুরি হয়। তাই সীমানা দেয়ালের বড় গাছগুলো কেটে ফেলা হয়েছে; যাতে চোর গাছ বেয়ে ওই পাশে যেতে না পারে!
এর আগে আছে ওয়াচ টাওয়ার। নিচের গেটে তালা লাগানো। বানর যারা পোষেন, তাদের একজন এলেন চাবি নিয়ে। ছয়-সাত তলা সমানের ওয়াচ টাওয়ারে উঠে ভয় লাগল কিছুটা। ভীষণ বাতাস। এই বুঝি সুপারি গাছের মতো দুলতে শুরু করবে।
এখান থেকে দেখতে দেখতে মনে হলো, পুরোটাই মলাট ভাবলে ভুল! ওপর থেকে পৃথিবী গোলাকার দেখায়। এ গোলকের ভেতর যেন পুরোটাই সবুজ গাছ, মাঠও আছে সবুজ! হরিণের খাঁচাটুকু সবুজ ঘাসের দ্বীপ। বনের অলিগলি যেন বিশাল কোনো পাতার হাতে থাকা রেখা।
এ সবুজ ঋতুতে ঋতুতে পাল্টায়। আবার গাছে গাছে আলাদা, পাতায় পাতায় আলাদা, মানুষে মানুষে আলাদা।
মোটে কয়েক মিনিট। এর মাঝেই নিচে নামার তাড়া দিতে থাকেন বন বিভাগের কর্মচারী। এ রকম একটা ওয়াচ টাওয়ারে ঘণ্টাখানেক বসে থাকলেও ক্লান্তি আসবে না। সময় থমকে দাঁড়াবে। যদিও একটু অস্বস্তি লাগবে। একটু একটু করে কখন যে নিজের দিকে ফিরে তাকাবে, বুঝতেও পারবে না কেউ।
আর দূর দেশের যে ছবি আমরা দেখতে চাই, তার পুরোটাই চোখের পাতায় ভর করে। তার মাঝে নিজেকেও পাওয়া যায়। হোক ক্ষুদ্র আমার এ অস্তিত্ব, সম্পর্ক তো ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে জোরদার। না, এভাবে হয়তো ব্যাখ্যা করা যাবে না! তার পরও যে বলতে চায় মন!
পাঁচ.
আমরা বনে ঢুকেছি দোখলা রেঞ্জ হয়ে, বের হওয়ার পথ রসুলপুরে। মোটরসাইকেলচালক ‘আল্লাহ হাফেজ’ জানিয়ে এখান থেকে বিদায় নিলেন। আমরা আবার বনে ঢুকলাম। ওই সময় বেশ হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল। চারদিক থেকে পাতা ঝরার শব্দে নীরবতার সনাতনী রূপ ছেড়ে নতুন করে মূর্ত হলো। হাওয়ায় পাতার শব্দে সাংগীতিক কোনো ছন্দ আছে কিনা জানি না, কিন্তু ভেতরে অদ্ভুত শূন্যতা জাগিয়ে তুলতে পারে। স্বস্তি আছে, মায়া আছে। ইউটিউবে রিলাক্সিং মিউজিক খুঁজতে খুঁজতে মাঝে মাঝে পেয়ে যাই বনের স্বর। আহা!
সেই শূন্যতার সিঁড়ি বেয়ে অবশ্য বেশি উপরে ওঠা গেল না। টানা মোটরসাইকেলে থাকার কারণে ছবি তোলা হয়নি। একটা গলিপথ ধরে ঢুকে গেলাম। ছবি তুলতে থাকলাম নানা ভঙ্গিতে। যাতে বন বন ভাবটা জোরদার হয়! নইলে যেন আমরাও পরে বিশ্বাস করব না বনে এসেছি।
এরপর টাঙ্গাইল সীমানা পেরিয়ে ময়মনসিংহ সীমান্তে ঢুকি, যার শুরুতেই জয়েনশাহীর মাজার। পাশের রাস্তা ধরে আমরা ভেতরের গ্রামে যেতে থাকি। রাস্তার দুই পাশে লেবুর বাগান। সুবাস ছড়িয়ে যাচ্ছিল। অনতিদূরে টিলার মতো ঢিবি চোখে পড়ছিল। আমার সফরসঙ্গী বলছিলেন, এগুলো নাকি আগে পাহাড় ছিল। পরে কেটে সমতল করা হয়েছে। আগের ভ্রমণে তিনি শুনেছিলেন।
এ পথ চলতে চলতে আমরা হাজির হলাম বানার নদীর ব্রিজে। সূর্য একদম মাথার ওপর। আরো দূরে কোথাও রাবার ও কমলার বাগান। যাব কিনা ভাবতে ভাবতে পরে সিদ্ধান্ত পাল্টানো হলো। ব্রিজ থেকে নেমে খানিকক্ষণ হেঁটে ভ্যানে করে ফিরতি পথে রসুলপুর। তারপর মূল রাস্তা ধরে পঁচিশ মাইল। সেই প্রথম দেখা বন। কোথাও কোথাও গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল ও পাশের জমিতে কিছু নেই। তারপর ভাবতে ইচ্ছে করে, মধুপুর বন শুধু মলাটই নয়, মলাট পেরিয়ে কত গল্প সাজানো আছে নৈঃশব্দ্যের বুকে। ফর্মার পর ফর্মা শেষ হয়— নৈঃশব্দ্যের গান ফুরোয় না। শুধু আমাদেরই সময় নেই তার ঐকতান ধরার, কান পাতার। তাই নৈঃশব্দ্যের ভূমিতে এঁকে দিই শূন্যতা ও অর্থহীনতা।
*লেখাটি বণিকবার্তার সাময়িকী সিল্পরুটে প্রকাশিত।