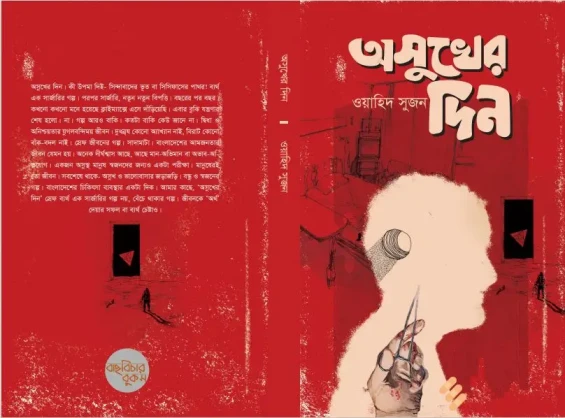(চৌচালা সৈকত, মাসখানেক আগে গিয়ে এ নামটাই শুনতে পাইলাম। কিন্তু এ লেখা যখন লেখা হয়— ২০১২ সালের অক্টোবর, তখন নামটা শুনি নাই। এ ৪-৫ বছরে জায়গাটার অনেক চেঞ্জ হইছে। পোর্ট বরাবর বড়সড় রাস্তা হচ্ছে, ওই রাস্তা দিয়ে বড় লরি চলবে। আগের রাস্তা নাই। নাই তারে সঙ্গ দেওয়া গাছগুলা। সেই নীরবতাও নাই। হয়তো সামনের কোনো গল্পে সে কথা বলা হবে। এ ভ্রমণ হয়তো ৫ বছর আগের। কিন্তু আবিষ্কারের অনুভূতি তো চিরকালের। নাকি!)

একটা ছড়ার কিনারায় বসলাম। জামার বোতাম খুলে দিলাম। এবার চোখ বন্ধ করে কান পেতে রইলাম। না, কিছু তো শুনা যায় না। হঠাৎ মৃদৃ একটা আওয়াজ পেলাম যেন। সাথে পাখির ডাক। আরো পরে নিয়মিত ছন্দে বাড়তে থাকে জোয়ারের উল্লাস। আসে আর যায়। কোথা থেকে আসে কোথা যায়! চোখ খুলতে হারিয়ে গেলো যেন। অক্টোবর ২০১২।
‘কাছেই জেলেপাড়া। এতক্ষণ এই আবাসস্থলের অস্তিত্বই বোঝা যায়নি। শ্রীহীন কয়েকটা শীর্ণ চালাঘর। খুব নিচু করে তৈরি। দূর থেকে স্তব্ধ কালো রেখার মতো দেখা যায়। এখন এই রেখার ওপর থেকে শাদা-কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেয়ে আকাশে উঠেছে। রান্নার আগুনে যেন সারা পাড়াটা প্রাণস্পন্দনে জেগে উঠল। জেলে-বৌরা ঝাঁকা নিয়ে আস্তে আস্তে পাড়া ছেড়ে নাউগুলোর দিকে আসছে। তাদের পেছনে উলঙ্গ শিশুর দল।’
এই বর্ণনা আল মাহমুদের ছোট গল্প ‘কালো নৌকা’ থেকে নেয়া। এই ক’টা লাইন মনে করিয়ে দেয় শান্তির মায়ের কথা। তার নাম জানি না। মেয়ের নাম শান্তি। এই নামে কোন মেয়ে ছিলো কিনা জানি না। তিনি মাথায় ঝাঁকা নিয়ে বাড়ি বাড়ি মাছ বিক্রি করতেন। যখন এই কাজ থাকত না ঝাঁকায় নিয়ে আসতেন বিস্কুট, কেকসহ নানা ধরনের বেকারি সামগ্রী। শান্তির মা বেঁচে আছেন কিনা জানি না। কিন্তু জেলে পাড়া এখনো আছে।
গিয়েছিলাম চট্টগ্রামের হালিশহর বি ব্লক জেলে পাড়ার পেছনের সৈকতে। আরো উত্তরে ফৌজদারহাট সৈকত। আল মাহমুদ একই গল্পে সে সৈকতের বর্ণনা দিচ্ছেন—
‘আকাশ পরিষ্কার থাকলে ফৌজদারহাটের বেলাভূমিতেও কম ভিড় হয় না। বেশ লোক জমে যায়। আজ রোববার বলেই যে এত গাড়ি আর মানুষের মেলা জমেছে তা নয়। মেঘবৃষ্টি না থাকলে প্রায় প্রতিদিনই মানুষ আসে। প্রাইভেট কারও আসে অনেক। আর মানুষের সমাগম দেখে কয়েকটা চায়ের দোকানও ডাঙার শুকনো উঁচু জায়গায় জমিয়ে ব্যবসা ফেঁদেছে। প্রতিদিন সূর্য নিভে গেলে পানির কিনারায় বহুদূর হেঁটে বেড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে মানুষ চায়ের দোকানগুলোতে এসে বসে। চা খায়। অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত আর উঠতে চায় না কেউ।’
কয়েকবছর আগে বন্ধুদের সাথে ফৌজদারহাট সৈকতে গিয়েছিলাম। এইখানে আছে সাঙ্গু গ্যাসক্ষেত্র এবং অন্যতম আকর্ষন গরম গরম কাকঁড়া ভাজা। দোকানদারেরা গরম গরম কাঁকড়া ভেজে দেয়। আমার বন্ধুরা বেশ মজা করে খেলো। আমি চিপস আর ম্যাংগো জুসে সন্তুষ্ট ছিলাম।
সৈকত বলতে সাধারণত কক্সবাজার, টেকনাফ, পার্কি এবং পতেঙ্গা-র নাম শোনা যায়। কিন্তু সীতাকুন্ড থেকে শুরু করে পতেঙ্গা পর্যন্ত অনেকগুলো বালির সৈকত আছে। বর্তমানে বড় অংশ গেছে জাহাজ ভাঙারিদের দখলে। রক্ষা পায় নাই উপকূল রক্ষাকারী ম্যানগ্রোভ বন। এখন চাইলেও শান্তির মায়ের বাড়ির কাছের সৈকত চাওয়া যাবে না। যাবে না জোয়ার আসাতক ফুটবল খেলা অথবা বেলাভূমিতে হৃদয় চিহৃ একেঁ নিজের নাম লেখা।

এরমধ্যে নিজের দড়িতে আটকে যাওয়া বাছুর আমাদের দিকে করুণ চোখে তাকায়। গরু এবং সাগর দুই দেখলে শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে আসে। অক্টোবর ২০১২।
কথা ছিলো সূর্য উঠার আগেই হাজিরা দেবো। কমপক্ষে পাঁচজন থাকার কথা। কিন্তু আলাপ শেষে বন্ধু দাউদের বাসায় ফিরতে ফিরতে আমরা দুইজন রইলাম। চট্টগ্রামের ঠাণ্ডা হাওয়ায় সমুদ্রের জন্য মন এমনিতেই আনচান করছিলো। ছোটবেলায় সমুদ্রের চেয়ে পাহাড় পছন্দ করতাম বেশি। পাহাড়ের নির্জনতা ও ধ্যানীভাব খুবই ভালো লাগত। কিন্তু আমার খুব কম বন্ধুরই পাহাড় ভালো লাগত। আমরা যেখানটায় থাকতাম, সেখানে পাহাড় আর সমুদ্রের দুরত্ব কিলো দুয়েক। পাহাড় আর সমুদ্র নিয়ে একটা মিথ আছে। ছোটবেলায় শুনতাম মাহবুবা খালার মুখে-
পাহাড় হলো বোন আর সমুদ্র হলো ভাই। কিন্তু কেউ কারো দেখা পায় না। তাদের মনে অনেক দুঃখ। পাহাড় সমুদ্রকে না দেখার যাতনায় অবিরত কাঁদতে থাকে। চোখের জল জমে ছড়া (পাহাড়ী প্রাকৃতিক নালা) হয়। ছড়ার জল এসে সমুদ্রে পড়ে। এইভাবে ভাইবোনের দেখা হয়। আর যেদিন সমুদ্রের কাছাকাছি পাহাড় এসে যাবে সেদিন হবে কেয়ামত।
ছোটবেলায় এই গল্প বিশ্বাস করতাম। কিন্তু এখন দেখি দুনিয়ার নানান জায়গায় সমুদ্র আর পাহাড়ের সহাবস্থান। এমনকি সাগর তলেও পাহাড়-পর্বত আছে। তবে এই গল্পের মূল্য কমে নাই। কোন এককালে সমুদ্র আর পাহাড় এক ছিলো, যেভাবে একই গৃহে লালিত পালিত দুই ভাই-বোন একসময় আলাদা হয়ে যায়। দুনিয়ার নিয়মই হয়।
সববিন্দু এসে সমুদ্রে মেশে। সে সমুদ্র দর্শনের দিন আমরা বেলা দশটা পর্যন্ত ঘুমালাম। কিন্তু জেদ চেপে গেলো যাবোই যাবো। সে মোতাবেক দ্রুত নাস্তা করে দৌড়। সে আবার মজার ঘটনা। দাউদের ১৯৬১ মডেলের ভেসপা চালু হতে সময় লাগল মিনিট দশেক। এরমধ্যে কিছু মহিলা প্যাচাল শুরু করেছে। পাঁচতলা থেকে কে যেন নীচে ময়লা ফেলছে। এটাও নৈসর্গিকতার মতো দেখার বিষয়। তবে মূলভাব বর্ণনাতীত।
চট্টগ্রামের অলংকার থেকে দেওয়ান হাটের রাস্তার বর্ণনাও বর্ণনাতীত। আপনি যদি চট্টগ্রামে যান ভুলেও এই রাস্তা মাড়াবেন না। কর্মব্যস্ত ঈদগাহের ভেতর দিয়ে নানান পথঘাট-সভ্যতা পেরিয়ে বারটা নাগাদ পৌছলাম গন্তব্যে। বেড়ি বাঁধের উপরে উঠার আগে চমৎকার একটা পথ ধরে আসতে হয়। দুইপাশের ফসলের ক্ষেত। অনেক ক্ষেত কাঁচা টমেটোয় ভর্তি। ঝাঁক বেধে বুনো পায়রা উড়ছে।
যে দোকানের চালে বানরের বাচ্চাটা বাঁধা, সেই দোকানে আমরা চা খেলাম।ঐ তো ঝাউ গাছ। সমুদ্র দেখা যায়। কয়েকটা বাচ্চা এসে বানরকে ক্ষেপানো চেষ্টা করছে। মানুষ কেন অ-মানুষ বা যাকে তার সমগ্রোত্রীয় মনে করে না তাকে ক্ষেপানোর চেষ্টা করে আমার কাছে বোধগম্য না। হয়তো মানবকেন্দ্রিক এই দুনিয়ায় মানুষ আর সবকিছুকে নিজের ভোগে লাগাবে মনে করে। আহা! সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই অথবা নিজেকে শ্রেষ্ট প্রমানের উপায় হলো কাউকে ছেড়ে কথা কইব না। একটা বাচ্চাকে দেখে দাউদ উক্তি করল-এই বাচ্চা বিবর্তনের ধাপ পার হয় নাই। কি বুঝল কে জানে। বলে উঠল- চুপ থাক। তারপর বন্ধুর সাথে দৌড়। সৈকতে। যেখানে সব নদী এসে মেশে। আমরা কিছুটা হতবাক। মজা পাই নাই তাই না। এইখান থেকে সরু পথে সৈকতে যেতে হয়। পথে দুপাশে ক্ষেতের মতো আল দেয়া। এখানে জোয়ার আসে। বেশ মাছ পাওয়া যায়। আসার সময় একটা সাপও দেখেছিলাম। মাথা ভাসিয়ে তাকিয়ে আছে।
শেফালী ঘোষের একটা চমৎকার গান আছে। ‘শঙ্খ নদীর মাঝি আই তোঁয়ার লগে রাজী’ এই লাইনটা শুনলেই কেমন যেন লাগে। মাঝির সাথে সে রাজি কেন? নদী আর জীবন দুটোর উৎসই পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠার। ক্ষুদ্র বিন্দু কি করে বিশাল সিন্ধু হয়ে উঠে। যেমন সব নদী সাগরে মেশে, মানুষ জনারণ্যে। এই মেশামেশির বাইরে তার আলাদা একটা রূপ আছে। তাকে খুঁজতে উৎসে ফিরে যেতে হয়। এই সমুদ্রের উৎস খুঁজতে আমরা তো নদীতেই যাবো। মনে করার চেষ্টা করি। সমুদ্র নিয়ে কোন গান মনে পড়ে কিনা। দেখি পড়ে না। কেন? আঞ্চলিক গানে নদী রহস্য, রোমান্টিকতা বা বিরহের আবহে আসে। এই নদীর দান তো কম নয়। মানুষ তার আবির্ভাবকাল থেকে নদীকে নানাভাবে কাজে লাগিয়েছে। সে তুলনায় সমুদ্রের বৈরীতা বেশি। তবে ভদ্রলোকী সাহিত্য, গান ও কবিতায় সমুদ্রের উপস্থিতি লক্ষ্যনীয়। হয়তো আমাদের হৃদয়ের বিশালতার একমাত্র তুলনা সমুদ্র। না, ওপরে তো নিখিল আকাশ আছে।
এই বাঁধ ধরে হাঁটলে মাইল চৌদ্দ কি পনের কি.মি. দূরে পতেঙ্গা সৈকত। এর আগে আছে কবি সৈয়দ আহমদ শামীমের বাড়ি। তার বাড়িতে ভাতের সাথে অদ্ভুত একটা পানীয় খেয়েছিলাম। নাম কাজিঁ। এরপর কোথাও আছে পতিতা পল্লী-চৌদ্দ নাম্বার। যার বিস্তারিত বর্ণনা আছে হরিশংকর জলদাসের উপন্যাস কসবি-তে। আছে সমুদ্রবন্দর, মেরিন একাডেমী এবং শাহ আমানত বিমানবন্দর।
চা খেয়ে আমরা দুই বালকের পিছু নিয়ে আরেকটা ছোট বাঁধে হাজির হলাম। এরপর অদ্ভুত সবুজের রাজত্ব। দূর থেকে মনে হবে সবুজ বিছানা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। বলছে, দেখ ঘাসের শয্যায় কতো মায়া। আরো চমৎকারিত্ব আছে। এই ঘেসোভূমি মাঝে মাঝে ছোট ছোট নালা। জোয়ারের পানিতে ভরে উঠছে। রাখালেরা গরু ছেড়ে গেছে। তারা মনের সুখে ঘাস খাচ্ছে। এরমধ্যে নিজের দড়িতে আটকে যাওয়া বাছুর আমাদের দিকে করুণ চোখে তাকায়। গরু এবং সাগর দুই দেখলে শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে আসে। বাল্যকালে গরু চরাতে যেতেন আর দুষ্টু ছেলেরা তাকে বিরক্ত করত। এই ভাব নিয়ে লালনের গোষ্ট রচিত হয়েছে। যা ভোরে গাওয়া হয়। এরমধ্যে অতিপরিচিত হলো- আর যাবো না গোষ্টে মাগো। বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের গায়ের রং নীল। এর তুলনা করা হয় সমুদ্রের জলের সাথে। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল আর কাছে গেলে স্বচ্ছ। কৃষ্ণ তেমন নিরঞ্জন। তবে এখানকার জলে কৃষ্ণ ভাব নাই। দূর থেকেও এ জল রূপার মতো। কাছে গেলেও তাই। এই জলের গভীরতা নাই। সমুদ্রের বাতাস এসে গা জুরিয়ে দিচ্ছে। আমরা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম কেওড়া গাছের তলে। কিছু জাহাজ দেখা যাচ্ছে। পণ্য খালাসের অপেক্ষায় আছে। আমরাও অপেক্ষায় আছি।
বেশ তো বিশ্রাম হলো। কি একটা গান শুনছিলাম। লালনের গান। লালনের একটা গানের লাইন আছে এমন- ‘ফকির লালন মরল জল পিপাসায় রে, কাছে থাকতে নদী মেঘনা’। ভাবের কথা বাদ দিলে কোথায় লালন আর কোথায় মেঘনা। তবে আসমান ফকির বলেছিলেন- কুষ্টিয়ার আশেপাশে কোথাও মেঘনা নামের নদী আছে। অন্যদিকে আমরা বলতে পারব না- ‘সুজন মরল জল পিপাসায় থাকতে বঙ্গোপসাগর’। না, রূপক মিলছে না। সাগরের জল তিয়াস মেটায় এমন নমুনা মার্কিন নৌবহর ছাড়া আর কোথাও নাই। সুতারাং, সে চিন্তা বাদ। আরো গভীরতর কিছু যেন। কি সেটা?
একটা ছড়ার কিনারায় বসলাম। জামার বোতাম খুলে দিলাম। এবার চোখ বন্ধ করে কান পেতে রইলাম। না, কিছু তো শুনা যায় না। হঠাৎ মৃদৃ একটা আওয়াজ পেলাম যেন। সাথে পাখির ডাক। আরো পরে নিয়মিত ছন্দে বাড়তে থাকে জোয়ারের উল্লাস। আসে আর যায়। কোথা থেকে আসে কোথা যায়! চোখ খুলতে হারিয়ে গেলো যেন। এক ঝাঁক পাখি ঢেউ ছুয়ে সরে সরে যাচ্ছে। আমাদের আশে পাশে পাখিরা খেলছে। একমধ্যে বক চিনতে পারলাম। আমরা কেউ কাউকে পরোয়া করলাম না। দুইয়ে মিলে রই মিশে। দুনিয়ার একদিকে মানুষ আর অন্যদিকে বাকি সব। হায়! এই ভেবে একা হয়ে যাই। দাউদ আফসোস করে বলল, শহরে এখন কাকও দেখা যায় না। একসময় শুনতাম কাক আর কবির সংখ্যা একই। এখন বোধহয় কবিই বেশি।

না। নাম আসগর আলী চৌধুরী মসজিদ। স্থাপিত হয়েছে ১৭৯৫ সালে। বর্তমানে সংস্কার চলছে। যেনতেনভাবে সিমেন্ট চুন লাগিয়ে কাজটা শেষ করা হয়েছে। আগের সুক্ষ কাজগুলো নষ্ট করে ফেলেছে। আফসোস করা ছাড়া কিইবা করার আছে। অক্টোবর ২০১২।
আমরা সৈকততক যাই নাই। দূরে বসে ঘন্টা দুয়েক পার করেছি। কাছে গেলে কি হবে। যে নিরঞ্জন তাকে তো ধরা যাবে না। আসার পথে ছড়ার পানিতে পা ভিজিয়ে নিই। জিয়ারত করি হাফেজ মনিরুদ্দীন (র.)-র মাজার। এরপর ফইল্যাতলীর বাজারের দিকে চলতে থাকি। পথে একটা মসজিদ চোখে পড়লে নামি। মোগল স্থাপত্যকলার অনুরূপ মসজিদ চট্টগ্রামে আছে জানা ছিলো না। নাম আসগর আলী চৌধুরী মসজিদ। স্থাপিত হয়েছে ১৭৯৫ সালে। বর্তমানে সংস্কার চলছে। যেনতেনভাবে সিমেন্ট চুন লাগিয়ে কাজটা শেষ করা হয়েছে। আগের সুক্ষ কাজগুলো নষ্ট করে ফেলেছে। আফসোস করা ছাড়া কিইবা করার আছে। যেখানে আসতে রাস্তার ঠিক নাই- সেখানে আবার পুরাকীর্তি। এই পথে পড়ে আন্ধা হাফেজের মাজার। হুমায়ুন আহমেদের ‘দেয়াল’ উপন্যাস উনার কথা আছে। তিনি লিখছেন-
‘টিনের বেড়া, টিনের চালা। ছোট্ট কামরা। দড়ির চারপাইয়ের এক কোনায় প্রচণ্ড গরমেও উলের চাদর গায়ে আন্ধা পীর বসে আছেন। চারপাইয়ের এক কোনায় বিশাল হারিকেন। হারিকেনের কাঁচ ঠিকমতো লাগানো হয়নি বলে বুনকা বুনকা ধোঁয়া বের হচ্ছে। বাতাসের কারণে ধোঁয়া যাচ্ছে আন্ধা পীরের নাকে-মুখে। তাতে তাঁকে বিব্রত মনে হচ্ছে না। চাদরের বাইরে তাঁর ডানহাত বের হয়ে আছে। হাতে মোটা দানার তসবি। দানাগুলোর একেকটির রং একেক রকম।’
তার মাজার জেয়ারত করলাম। সেই টিনের বেড়া, টিনের চালা এখন আর নাই। সুন্দর গম্বুজবিশিষ্ট সুপরিসর কক্ষে তার কবর। জেয়ারত করলাম ফইল্যাতলীর তিনটি মাজার। এদের মধ্যে দুজন হলেন হযরত বশীর আহমেদ শাহ (র.) এবং হযরত জারীফ আলী শাহ (র.)। ইনারা দুজন ভাই এবং বেয়াই। দুপুরের খাবার খেলাম তাদের এক নাতীর সাথে। পথে পাড় হলাম অনেক মসজিদ আর মাজার। ইতিহাস থেকে ক্রমে যেন পিছলে যাই আর ফিরে আসি। ফিরে আসায় নিয়তি।
এই হলো দইজ্যার পাড় ঘুরা। চট্টগ্রাম থেকে ফিরে ভাবছিলাম এই ঘুরাঘুরি আমায় কি দিলো। তা বর্ণনা করতে পারব না। তবে অনুভূতির চেয়ে কে আছে ভালো বন্ধু। ফেসবুক স্ট্যাস্টাসটা দেখানো যেতে পারে-
দইজ্যার (সমুদ্র) কুলে গেলেই হয় না, কলিজার ভেতর দইজ্যারে ধারণ করতে হয়। দইজ্যার মতো কলিজার অধিকারী কয়েকজনের সাথে এই কটা দিন কাটালাম। তাদের জন্য অশেষ ভালোবাসা ও প্রার্থনা।
*লেখাটা সে সময় পরিবর্তন ডটকমে প্রকাশিত হয়। লিখিয়ে নেওয়ার কৃতিত্ব অনেকখানি রওশন আরা মুক্তার, যিনি ওই পোর্টালের বটতলীর আসর নামক জনপ্রিয় পাতা পরিচালনা করতেন।