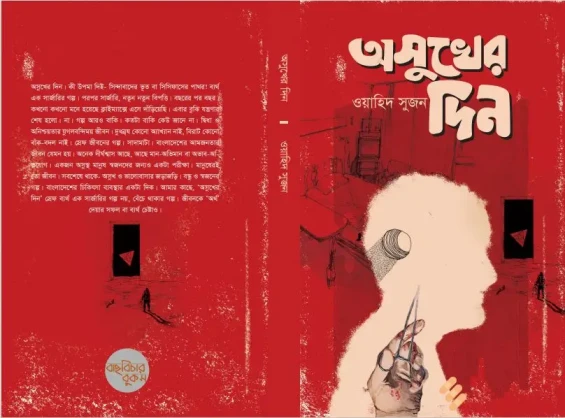হাওরের মাছ কোথায় যায়
ইলিয়াস কাঞ্চনের মালিকানাধীন প্রভাতী হোটেল কাম স্টুডিওতে দুপুরের খাবারটা সেরে নিলাম। আমি নিলাম কাচকি, অন্যদের জন্য শোল ও বেলে মাছ। শিং মাছের সাইজ নিয়া দারাশিকো ভাইয়ের দারুণ আপত্তি। মাছের দেশে মাছের সাইজ নিয়া অত্যাচার! পরে দেখা গেল, কুলিয়ার চরে যে যে মাছ দেখেছিলাম— তা হাওরের মধ্যিখানের অষ্টগ্রামের দুই হোটেলে পাওয়া যায় না। মানুষজন বাড়িতে কী রাঁধে জানার ইচ্ছে থাকলেও জানা হল না। হয়ত হাওরের মাছ শহরে চলে যায়, স্থানীয়রা খায় চাষের হাইব্রিড!
খাওয়া শেষে বিল দিতে দিতে দেখার কী আছে প্রশ্নে কুতুব শাহী মসজিদের নামই জানলাম, যার নাম অষ্টগ্রামের খোঁজ-খবর নিতে গেলে সেধেই জানাবে নানা মাধ্যম। আর কী আছে? বারো আউলিয়ার দেশ এই অষ্টগ্রাম। অন্য আউলিয়া কারা? একজনের নাম জানানো হল। উনার মাজার পূর্ব অষ্টগ্রামে। নাম ভুলে গেছি। ক্যাশ কাউন্টারের পেছনে সাদা দাড়িশোভিত জোব্বা পরা একজনের ছবি দেখে জিগেশ করলাম, উনি কে? জানালেন, পীর। মারা গেছেন। বাড়ি পাকিস্তানে।
মসজিদের খোঁজে বাইর হয়ে একটা মিষ্টি দোকানে ঢুকলাম। তিনজনে মিলা দুইপদ ট্রাই করে বোঝা গেল কাজের না। ঢাকার বাইরে এমন অকাজের অভিজ্ঞতা কমই হইছে। দুই-তিনটে রিকশা দরাদরি করে কুতুব শাহ মসজিদ দেখার চালক পাওয়া গেল। বলে রাখি, এই অঞ্চলের সব রিকশাই মটরে চলে! হাওরের ধারে বাধাই রাস্তায় তরতর করে চলে। পানি বাড়লে রাস্তার ধার পর্যন্ত চলে আসে।
বারো কেন?
আমার যেখানে বেড়ে ওঠা ওই জায়গার নামও বারো আউলিয়া। এ নামে মাজারও আছে। চট্টগ্রামকে বলা হয় বারো আউলিয়ার দেশ। অষ্টগ্রামেও শুনছি বারো। কেন?
উত্তর জানি না। তবে ভাবতে ভাবতে মজার কিছু বিষয় মাথায় আসল। ১২টা রাশির কথা জানি। ১২টা মাসের কথা জানি। হযরত ইয়াকুব (আ.) এর ১২ সন্তানের কথা জানি। যাদের থেকে এসেছে ইহুদীদের বারো গ্রোত্র। এর মধ্যে কিছু গ্রোত্র হারিয়ে গেছে। যার একটার সন্ধান ভারতে পাওয়া গেছে।
আবার ধরেন হযরত শাহজালাল (রা.) যখন দিল্লি আসেন আরব থেকে তার সঙ্গে ছিল ২৪০ জন শিষ্য। অন্যদিকে তরফ (সিলেট) রাজ্যে আসার সময় উনার শিষ্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬০ জন। দুটোই ১২ দিয়ে ভাগ করা যায়।
প্রেসিডেন্টের এলাকা বলে কথা
রাস্তার পাশে খাল মতো জলায় চড়ছিল হাঁস। শত শত। কোথাও কোথাও রাজহাঁস। কোথাও কোথাও কাল্পনিক খাকি ক্যাম্বল। স্মৃতি থেকে এ নামটা আসলেও সত্য কিনা জানি না।
চলতে চলতে একটা-দুটা স্কুলঘর পার হওয়া লাগল। হাওরের মাঝ দিয়ে বিদ্যুতের খুঁটি দেখেছিলাম, আরো কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে সোলার প্যানেল। এ প্রসঙ্গে এনজিও’র প্রসঙ্গ আসলো। নিশ্চয় ব্র্যাক অগ্রগণ্য হবে। রিকশাচালকও প্রথমে ব্র্যাকের নাম বলছিলেন। প্রথমটাই খেয়াল করি নাই। উনিও আগে কয়েকটা এনজিও থেকে লোন করেছিলেন। এখন ব্র্যাকে লোন আছে। লোন নিয়া লোকে কী করে? উত্তরে জানান, সাধারণত আগের কর্জ শোধ করে, ঘরদোর করে, আসবাবপত্র কেনেন। লোন নিয়া লোন শোধের এ চক্র আপনি সারা বাংলাদেশে পাবেন। ফলস্বরূপ অনেককে দেখেছি ভিটা-বাড়ি ছেড়ে শহরের পোশাক কারখানায় চাকরি নিতে। তখন সংসারের ভার অনেকটাই চাপে পরিবারের মেয়েদের উপ্রে।
শোয়াইব মজা করে বললেন, প্রেসিডেন্ট এলাকার মানুষ চাকরির অভাব নেই। এবার ক্ষেপেই গেলেন চালক, ‘বড়লোকের জন্য বড়লোক। যারা উনার আশপাশের সোফায় বসে থাকেন। তারাই সব পান।’ সেই অমিয় বাণী— গরীবের তরে কেউ নাই!
পথের শেষে…
অষ্টগ্রাম আসার সময় আমাদের সঙ্গে লঞ্চে ছাদে এক তরুণের সঙ্গে পরিচয়। জানান, আমাকে চেনা চেনা লাগছে। কেন লাগছে? এর উত্তর আমি বা উনি দিতে পারলাম না। জানতে চাইলেন, অষ্টগ্রামে কী আমাদের পরিচিত কেউ আছে। শোয়াইব জানালেন, কেউ নেই। তবে ফেসবুকে এ এলাকা নিয়া অনেক পোস্ট দেখেছি। উনাকে কয়েকবার জিগেশ করতে প্রতিবারই বললেন, নাম ‘পথের শেষে..’। অবশেষে বলতে হলো, ভাই ফেসবুক না সত্যিকারের নাম বলেন।
কথাবার্তায় জানা গেল উনার ভাই বিমানবন্দরে চাকরি করেন। প্রেসিডেন্টের দেওয়া চাকরি। আমাদেরও অনুমান সরলীকরণ হলো। ওইটা নিয়াই ক্ষেপলেন রিকশাচালক। তবে এটা ঠিক যে ঝা ঝা চকচকে রাস্তা বা বিশাল সেতুর রহস্য এখানেই।
কে বানালো কুতুব শাহী মসজিদ?
আসরের কাছাকাছি সময়ে কুতুব শাহী মসজিদে পৌঁছলাম। সূর্য তখন পশ্চিমে মানে মসজিদের পেছনে। তাই এক ধরনের অস্বচ্ছ আভা বের হচ্ছিল। সামনে থেকে ছবি তুলতে গিয়া সুবিধা হল না। দরোজায় তালা থাকায় ভেতরে ঢোকাও হলো না। মূল দরোজার সামনে বসে আছেন এক বয়স্কা নারী। পরনে সবুজ ছাপার শাড়ি। চোখে জল নিয়ে দুই হাত জড়ো করে কিছু চাচ্ছেন। এরপর মসজিদের পেছনে গিয়া মনে হল এটা পরে সংস্কার হইছে। আমার ও শোয়াইবের তেমনই ধারণা। দারাশিকো ভাই উল্টোই ভাবলেন। এ ধরনের প্রাচীন স্থাপনা অনায়াসে ৩-৪শ বছর টিকতে পারে। আমাদের একটা যুক্তি ছিল এমন ধরনের স্থাপনায় অনেক কারুকাজ থাকে। এখানে দেখা যাচ্ছে না। বাইরের ইট নতুন মনে হচ্ছে। তার উপ্রে কোণা-কাঞ্চিতে দুই-একটা নকশা দেখা যাচ্ছে। হয়ত নমুনা হিসেবে রাখা হইছে।
মসজিদের দক্ষিণ পাশে তিনটে উঁচু করে বাঁধানো কবর। মানুষগুলান অনেক লম্বা ছিলেন নিশ্চয়। কবরের সামনে মোমবাতি দিল কয়েকটা বাচ্চা। ভাবছিলাম কোনটা কুতুব শাহের কবর? পরে দেখা গেল পেছনে মহাসমারোহে সাজানো-গোছানো মাজার। জেয়ারত করতে গিয়া দেখি কয়েকজন নারীই আছেন শুধু। তারা যেভাবে ভক্তি করছিলেন অস্বস্তি লাগায় শুধু সালাম দিয়ে ফিরে আসার পথে সবজে শাড়ি পরা সে নারীকে দেখলাম। মনে হলো বয়স অনেক কম!
ফের মসজিদের সামনের চত্বরে দাঁড়ায়া আমরা সংস্কার হওয়া-না হওয়া নিয়া তর্ক করতে থাকি। ওই সময় রিকশাচালক এসে বলেন, এ মসজিদ কেউ তৈরি করেন নাই। মাটি ফুঁড়ে বের হওয়া। আমরা তর্ক থামিয়ে দিলাম। এভাবে তর্ক বিষয় সীমানা মিলল। আমরা খুব্ই ভাগ্যবান নিশ্চয়।
অষ্টগ্রাম উপজেলা ওয়েবসাইট জানাচ্ছে, ৩০০ বছর বয়সের দৃষ্টি নন্দন এ মসজিদ নিয়ে সাধক অলি কুতুব শাহ রহমত উল্লাহর অনেক কেরামত ও ধর্মীয় ভাব-আবেগের কথা লোকশ্রুত রয়েছে। মসজিদের পূর্ব-পশ্চিমে শায়িত হযরত শাহজালাল ইয়ামিন উল্লাহর সফর সঙ্গী হযরত শাহ কুতুব রহমত উল্লাহের নাম অনুসারে এ মসজিদের নামকরণ করা হয়েছে। বাংলায় সুলতানী ও মুঘল আমলের কারুকার্যে বৈশিষ্ট্যে স্থাপিত পাঁচ মসজিদের স্থাপত্যকাল নিয়ে ইতিহাসবিদদের মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ ষোল শতাব্দীর নির্মিত বললেও অধিকাংশের মধ্যে মতে এ মসজিদ ১৭০০ শতাব্দীতে নির্মিত। মসজিদের দেয়ালে স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যে প্রমাণিত সতের শতাব্দীর প্রথম দিকে সুলতানী ও মুঘল স্থাপত্যের নজীর।
এখানেও উকিল মুন্সী
পরে আমরা যখন ফিরছিলাম কোথাও একটা রাস্তার নাম দেখলাম সৈয়দ সৈয়দ নাসিরউদ্দিন সিপাহশালার সড়ক। উনি হজরত শাহজালালের শিষ্য। দিল্লির বাদশার আদেশে গৌর গোবিন্দকে পরাজিত করতে আসছিলেন। পথে শাহজালালের দেখা পেয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নাসিরউদ্দিনের বংশধররা বসবাস করেন পাশের জেলা হবিগঞ্জে। তাদের পীরায়ালি এখনো জারি যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে অষ্টগ্রামেও তার একটা প্রভাব আছে।
নাসিরউদ্দিনের বংশেই জন্মগ্রহণ করেন উকিল মুন্সীর পীর। পাশের কোথাও ইটনা বলে একটা জায়গা আছে। ওই জায়গায় ঠাকুর বাড়ি নামের এক বাড়ি আছে— সেখানে উকিল মুন্সীর শৈশবের অনেকটা সময় কেটেছিল। বাবা মরা, মায়ের বিয়ে হওয়া অনাথ ছেলেটা নিশ্চয় অনেক বিষণ্ন মনে ঘুরে বেড়াতেন। ঘোরাঘুরির মাঝে ছোয়াচে ব্যাপার আছে— তা হলো বিষণ্নতা। অন্তত হাওর তেমনই দিশা দেখায়। বিকেলের হাওয়ায় তেমন কিছু ভর করে। আরো অনেক পরে সে হাওয়ায় ভর করে আমরা বসে থাকি হাওরের পারে। আর হাওরের জলের খবরই দিয়ে গেছেন উকিল মুন্সী।
জঙ্গল শাহ
মসজিদের সামনের রাস্তা পার হয়ে পুকুরপাড় ধরে জঙ্গল শাহর মাজারে যাওয়া যায়। এ মাজারটি হিন্দু বাড়ির মাঝে অবস্থিত। ভক্তির ব্যাপার এখানে বরাবরই আন্তঃধর্মীয়। জঙ্গল কেটে মাজারটি আবিস্কার করায় এমন নাম।
সাধারণত বটজাতীয় গাছ দেখা যায় মাজারের কেন্দ্রে। এখানে আছে বিশাল একটি কড়ই গাছ। যেমন মোটা, তেমনি উচ্চতা ও ছড়ানো। রিকশাচালক জানালেন গাছটি কাটার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু কী যেন ঘটছিল (আমিই ভুলে গেছি) তাই কাটা সম্ভব হয় নাই। ফিরতি পথে দেখলাম কুতুব শাহী মাজার থেকে কিছু নারী এদিকে আসছেন। যেহেতু শুক্রবার— তাই হয়তো একদিনে সবগুলো মাজার ঘোরার জন্য চমৎকার একটা দিন। ছোটবেলায় এক খালার সঙ্গে কালু শাহ ও আমানত শাহর মাজারে গেছিলাম এক ভাইয়ের পরীক্ষার আগে। সে রকমই হয়তো!
জঙ্গল শাহ শুনে ঈশা খাঁর জঙ্গল বাড়ির কথা মনে পড়ছিল। স্বাধীন চেতা হিসেবে ময়মনসিং অঞ্চলের অন্যরকম সুনাম আছে। প্রবল প্রতিপত্তিশীল মুঘলদের সঙ্গে লড়াই ও চাতুরিতে স্মরণীয় নাম বারো ভুঁইয়া। যাদের একজন ঈশা খাঁ। পরদিন আমরা জঙ্গল বাড়িতে ঈশা খাঁর স্থাপনার ভগ্নাবশেষ দেখতে গিয়েছিলাম। আরো দেখতে গিয়েছিলাম স্বাধীনচেতা নারী কবি চন্দ্রাবতীর বাড়ি।
স্থানীয় উল্লেখযোগ্য খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে রয়েছে পনির। দারাশিকো ভাই হদিস নিতে গেলে রিকশাওয়ালা একটা দোকানে নিয়া গেলেন। পনির সম্পর্কে আমার ধারণা নাই। কিনেছিলাম একবার মাত্র। রেসিপি বলতে জানি— কেকা ফেরদৌসীর পনিরের বল। তো, দোকানদার জানালেন অর্ডার দিলে পরদিন সকাল নাগাদ পাওয়া যাবে।
আসলে হচ্ছে কী? আমরা ঘুরতেছিলাম। ভালো লাগতেছিল। কিছুই মনে রাখারই যেন দরকার নেই। এরপর আরেকটা মাজারে গেলাম। উনার নামটি বেশ কয়েকবার জিগেশ করেছিলাম। মনে নাই একদম। উনার মাজারও বেশি পুরনো না। যিনি খাদেম ছিলেন আমাদের বেশ খাতির করলেন।
যাই হোক, আবারো ফিরতে শুরু করলাম আগের পথে। একটা বাজার পড়তে ২০টা কলা কেনা হলো ৪০ টাকায়। খুব বেশি মজা লাগে নাই। উল্টো মজা হলো একটা যমজ কলা দিয়া। যেটা কেউ না খেয়ে রেখেই দিচ্ছিলো। সাবাড় হলো পরদিন।
ধুয়ে যাচ্ছে জুতোর কালি
কুলিয়ার চর থেকে সকালে যখন লঞ্চে চড়ি (স্টিমার বলতে পারলে খুশি হতাম) জানতাম ভাড়া ৯০ টাকা। ভেতরে জায়গা পাই নাই বলে ছাদেই বসা হলো। যাত্রীদের সঙ্গে ছিলেন চা-চানাচুরওলা। ছিলেন একজন মুচি। উনাকে দেখে নিজেকে সৌখিন মানুষ মনে হলো। যদিও ১০ মাসে একবারও পায়ের স্যান্ডেল জোড়া পলিশ করা হয় নাই। আরে পরিস্কার করা হইছে কতবার তাও বলা যাবে! যাই হোক, আয়েশ করে বললাম— দেন পলিশ কইরা। খালি পা পাঠাতনে রাখতেই ছ্যাৎ করে উঠল। এত গরম! পরে অবশ্য একটা ঝামেলা হলো। দারাশিকো ভাই দিছিলেন কাপড়ের জুতোটা সেলাই করতে। এই লোক বেশি কারবারি করে কাপড়ের উপর রং দিয়া পালিশ শুরু করল। সে জুতো শুকাতে শুকাতে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগছে। পরে টাকা নিয়াও সে গোলমাল করল। যাইহোক, আমাদের ভাড়া নিল ৬০ টাকা করে। আসার পথে জানলাম রোমান্টিক ভাব নিয়া ছাড়া উপ্রে বসে তাদের এ ভাড়া। চেয়ারের সাহেবদের জন্য ৯০ টাকা। ওই চেয়ারে বসার কারণে ফেরার পথে হাওরের ঝড় মিস করলাম। ঘুমায়া ছিলাম তিনজনই।
আচ্ছা। এ কথাগুলো কেন বললাম? আমার কাছে পরে মনে হচ্ছিল— এই যে চাকরি-বাকরি শেষে আহা-উহু টাইপ সৌন্দর্য দেখার জন্য ঘোরাঘুরি এটা আসলে কী! আমার ধারণা খানিক ছাপ রেখে জুতোর কালির মতো মুছে যায়। বেশি ব্যক্তিগত হয়া যায় তারপর বলি— পলিশ করা চাকচিক্যটা আসল না। তাই হয়ত ভালো লাগে না। এই সব ভ্রমণের স্মৃতি একসময় ফিকে হয়ে যাবে। মেবি মাসখানেকও লাগে না। মনে পড়লে সত্য মনে হয় না। তারপরও কিছু থেকে যায় সবসময়। ওইটাই আমার পাওয়া— ধুয়ে যাচ্ছে জুতোর কালি! সেটা কী?
এমন রাত কখনো আসে নাই
দারাশিকো ভাই উপরের দিকে তাকায়া বললেন, ‘দেখেন কত ঘামাচি’। আকাশ কার শরীর?— সে প্রশ্ন না করেই হাসতে হাসতে দম বন্ধ হওয়ার যোগাড়। এমন তুলনা কখনো শুনি নাই। তখন আমরা হাওরের পার থেকে উঠে আসছি সবে। অনেকক্ষণ বসেছিলাম। তার আগে খানিক লাঠি খেলা দেখলাম। এক বুড়োলোক অনেকগুলা বাচ্চাকে খেলা শেখাচ্ছিল। লোকজন তাদের চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়ায়া।
সন্ধ্যা ঘনায়া আসার সময়টা কত অপূর্ব। চারদিকে লালিমার ছটা। আমাদের পেছনে রাস্তার পাশে একজন লোক নামাজ পড়ছিল।
হাওরের পানির শব্দ বাড়ছে, নৈঃশব্দ্যে ভর করে। এরই মাঝে দুই-চারটে নৌকা ইঞ্জিনে ডাক তুলে ছুটে যাচ্ছিল। আর পশ্চিমের দুটা তারা। একটা বোধহয় শুকতারা। অন্যটা কী? আমার খানিকটা ভ্রম হচ্ছিল। অনেক আগে যখন অনেক রাত পর্যন্ত আমি আর মিশু হাঁটতাম। একটা তারা নিয়ে গল্প করতাম। ওইটা ছিল লুব্ধক।
ডাকবাংলো হয়ে দক্ষিণ অষ্টগ্রামের রাস্তা চলে গেছে। বিশাল একটা ব্রিজ আছে সামনে। আসার পর থেকে ওই ব্রিজে যাবো যাবো একটা ব্যাপার ছিল। তারপর গেলাম… রাতের খাবারের পর। তখন ১০টার মতো বাজে। আমরা তিনজান হাঁটছিলাম। এত অবিশ্বাস্য রাত আগে কখনো আসে নাই। দিগন্ত অনেক নিচে, আকাশের বিস্তার ছিল ধারণাতীত। আকাশ জুড়ে নক্ষত্র, ছায়াপথ। ছায়া ছায়া, ধোঁয়া ধোঁয়া, মিটমিট। আমরা হাঁটছিলাম আর তাকায়াছিলাম নিখিলে। এতটা ভালো লাগা অনেকদিন আসে না। শুকরিয়া।
হাওয়াও ছিল বেশ। সব ছাড়িয়ে অনন্তের কাছে একা হয়ে বসা থাকা। মনে হচ্ছিল এইখানটায় দাঁড়িয়ে থাকা বা হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর
কোনো কাজ নাই। মাঝে মাঝে গুণগুণ করছিলাম ‘আকাশ প্রদীপ জ্বলে’। দূরে কোথাও বাজনা শোনা যাচ্ছিল। কান পেতের সুর শুনি …‘নবী মোর পরশমনি, নবী মোর সোনার খনি’।
আহা, এমন রাত আর আসে নাই!