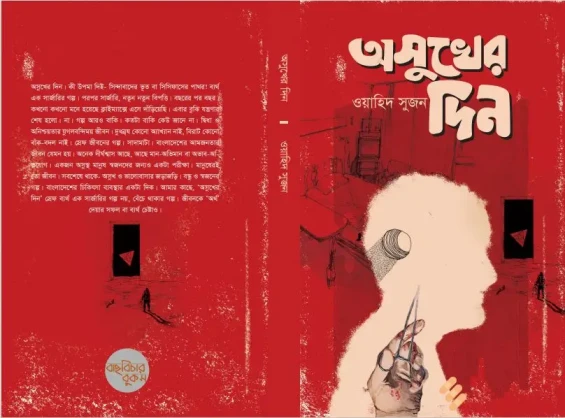ভ্রমণটা ছিল বেশ লম্বা। গাইবান্ধা হয়ে কুড়িগ্রাম, সেখান থেকে লালমনিরহাট ঘুরে নীলফামারী। এরপর ঢাকায় ফিরব। যাত্রার কয়েক দিন আগে অফিসের ক্যান্টিনে খেতে বসেছি, কথা উঠল ভ্রমণ নিয়ে। পাশ থেকে একজন বললেন, ‘গাইবান্ধা গেলে বালাসী ঘাটের রেল ফেরি দেখে আইসেন।’ এমন ধারার ফেরির কথা আগে শুনি নাই। আবার গাইবান্ধা পৌঁছতে পৌঁছতে ভুলেও গেলাম।
এক.
বালাসী ঘাট যখন পৌঁছলাম, তখন আড়াইটার মতো বাজে। ঘণ্টা দেড়েক আগে এসকেএস ইনের ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দুপুরে কোথায় খাব। আমাদের পথ প্রদর্শক শাহাদাত হোসেন মিশুক ভাই বলেন, ‘বালাসী ঘাটে।’ তখনই মনে পড়ল রেল ফেরির কথা।
পৌঁছতে পৌঁছতে খিদে লেগেছে বেশ। তাই দেখাদেখির আগে যমুনা নদীর তীরঘেঁষা একটা হোটেলে ঢুকে গেলাম। দর-দামের কথাও মনে ছিল না। ডালের বড়া, সবজি, চিংড়ি আর দুই পদের ছোট মাছ দিয়ে ভাত খেলাম তৃপ্তি নিয়ে। বড় মাছও ছিল, আমরা নিলাম না। নদীর বাতাস আসছিল ছোট ছোট কয়েকটা গাছ ছুঁয়ে। খিদে-ক্লান্তির পর খাওয়া-দাওয়া। এবার একটু ঘুম হলে মন্দ হয় না। তা যদি হয় নদীতীরে। বাহ! না, সে অবসর নেই আমাদের।
একটু পেছনে ফেরা যাক। বরাবরের মতো রাতের গাড়িতেই উঠেছিলাম ঢাকা থেকে। দু-তিন জায়গায় জ্যাম, দুবার চাকা পাল্টানো মিলে সকাল ৯টার দিকে গাইবান্ধায় নামিয়ে দিল গাড়ি। নাশতা করতে করতে আমাদের পিক করলেন মিশুক ভাই। পেশায় সাংবাদিক তিনি। আমাদের আশপাশে ঘুরিয়ে দেখাবেন। জানিয়ে রাখলাম, রাতেই যেতে চাই কুড়িগ্রামে। এখানে রাত কাটানোর তেমন ইচ্ছে নেই। উনি জানালেন, গোবিন্দগঞ্জ ঘুরে যেতে হবে। ওইদিকে রাস্তার কাজ চলছে। তাই ভ্রমণ হবে দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর। তখনই মাথায় এল অন্য পরিকল্পনা। জিজ্ঞাসা করলাম, ম্যাপে দেখেছিলাম গাইবান্ধা-কুড়িগ্রামের সীমানায় বিশাল নদীপথ। ওই পথে কি যাওয়া যাবে?
যাই হোক, প্রথমে আমরা গেলাম এসকেএস ইন রিসোর্টে। সেখান থেকে ফ্রেন্ডশিপ সেন্টারে। এটা আবার স্থাপত্যকলার দারুণ এক নজির। মাটির নিচে পুরো রিসোর্ট। দুটোই এনজিওর মালিকানাধীন। আর গাইবান্ধার দেখাদেখির অন্যতম স্পট এখন।
সেদিন আকাশে ছিল সাদা মেঘের আনাগোনা। উজ্জ্বল তুলোর মতো ঝিলিক দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। যদি কালো মেঘ এসে যায় হঠাৎ, তবে মিহি বৃষ্টিও হচ্ছে থেকে থেকে। ভাপসা গরমের মধ্যে চলছিলাম বালাসী ঘাটের দিকে।
বালাসী ঘাট খুবই ব্যস্ত এলাকা। ঘাট থেকে মানুষ আর মালপত্র বোঝাই নৌকোগুলো দূরে ছড়িয়ে পড়ছিল। কোলাহল, ইঞ্জিনের শব্দ আর নদীর নৈসর্গিক দৃশ্য মিলে একটা চিত্র কল্পনা করে নিতে পারেন। কেমন হতে পারে বালাসী ঘাট? আর যখন রেল ফেরি ছিল, তখন নাকি আরো জমজমাট ছিল।
এ রকম একটা ঘাটে নানা কিসিমের মানুষ চোখে পড়ে। থাকে নিত্য পারাপারের যাত্রী, স্কুল-কলেজপড়ুয়া, মালামাল খরিদ করতে আসা দোকানি, এনজিওকর্মীসহ কত ধরনের মানুষ। সেদিন দেখলাম কোনো একটা এনজিওর প্রোগ্রামে আসা কয়েকজনকে। তাদের টি-শার্ট দেয়া হয়েছে। হাতে একটা করে গাছ।
এবার রেল ফেরির একটা পরিচয় দেয়া যাক। ওইপারে জামালপুরের বাহাদুরাবাদ ঘাট আর এপারে বালাসী ঘাট। ১৯৩৮ সালে ব্রিটিশ সরকার ঢাকার সাথে উত্তরাঞ্চলের রেল যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে চালু করে এ রেল ফেরি। অবশ্য তখন এর ঠিকানা বালাসী ঘাট ছিল না ।
গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলায় তিস্তামুখ ঘাট ও জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জের বাহাদুরাবাদ ঘাটের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদে রেল ফেরি সার্ভিস চালু হয় ওই সময়।
জেলা তথ্যভাণ্ডার জানায়, এ ঘাট বা নৌবন্দরের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে এমনকি বিদেশেও মালামাল পরিবহন করা হয়। একসময় ফুলছড়ি ঘাটে ভিড়ত বড় বড় জাহাজ, লঞ্চ, স্টিমার। ইংরেজ লর্ডরা গাইবান্ধার নাম না জানলেও জানতেন ফুলছড়ি ঘাট।
এ ফেরি সার্ভিস যাত্রা করেছিল আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের অধীনে। ফেরির লাইনের সংখ্যা ১৩ এবং একেকটি লাইনে তিনটি করে বগি বা ওয়াগন নেয়া যায়। ১৯৯০ সালের দিকে যমুনা নদীর নাব্যতা কমে আসে। তখন ফেরি সার্ভিসটি তিস্তামুখ ঘাট থেকে বালাসী ঘাটে স্থানান্তর করা হয়। সময়ের পরিক্রমায় শুধু বাহাদুরাবাদ ঘাটই নয়; ব্রহ্মপুত্র ও যমুনার আরো ১০৪টি আন্তঃজেলা ও অভ্যন্তরীণ নৌ-রুট বন্ধ হয়ে গেছে।
রৌদ্রোজ্জ্বল এই দিনে বালাসী ঘাটে প্রাণচাঞ্চল্যের অভাব নেই। ঘাটের দৃশ্যগুলোর মধ্যে মনোহর লাগে একই রঙের ইউনিফর্ম ছাত্র-ছাত্রীদের। একবার নেত্রকোনার দুর্গাপুরের সোমেশ্বরীর ঘাটে গেরুয়া রঙের পোশাক পরা একদল বালিকাকে নামতে দেখি। তখন আকাশ ছিল আলোয় আলোয় ভরা। তাদের উপস্থিতিতে সবকিছু গেরুয়া বর্ণ ধারণ করে। ওই দৃশ্য ভোলার মতো নয়। ঘাটে এলে সে দৃশ্য হানা দেয় মনে। এখানেও বিচ্ছিন্নভাবে চোখে পড়ে ইউনিফর্ম। আর নৌকাগুলো জলের বুকে রেখা এঁকে এগিয়ে যাচ্ছিল দূরের কোনো চরে।
ফেরিঘাট দেখতে আমরা একটা পথ ধরে এগোলাম বাড়িঘরের ভেতর দিয়ে। মূল রাস্তা নদী খেয়ে ফেলেছে। কিছু পাওয়ার আশায় একটা বাচ্চা ছেলে আমাদের পিছু নিল। ঘ্যান ঘ্যান করছিল। বাড়িঘর পেরিয়ে আবার নদীর ধারে ফিরলাম, সেখানে একদল বাচ্চা পানিতে খেলছে। আমাদের সাথে আসা ছেলেটা আর দেরি করল না। জামা খুলে পানিতে ঝাঁপ দিল। কী দুরন্ত ব্যাপার!
এ ঘাট বা নদীর পাড় ধরে হাঁটলে নানা ধরনের নৌকা চোখে পড়ে। ছোট-বড়, ছৈ আছে, ছৈ নেই। দুপুরের এ সময়টা বিশ্রাম, গল্প বা নদীতে দাপাদাপি করে পার করছে অনেকে। কিছুদূর এগোতে দেখা গেল, ত্রিকোণ বাঁশ ফ্রেমে বাঁধা জাল পানিতে নেমে যাচ্ছে। আর উঠে আসছে মাছ ছাড়াই। তার পরই রেল ফেরি। জানা গেল, বছরের পর বছর এগুলো অযত্নে-অবহেলায় পড়ে আছে। আর কর্মচারীরা শুয়ে-বসে সময় কাটাচ্ছেন। অবশ্য সর্বশেষ খবরে জানা গেল, ফেরিঘাটকে সচল করতে সরকার বিশাল পরিকল্পনা নিয়েছে।
রেল বা ওয়াগন ফেরি ব্যাপারটা আমরা পুরোপুরি এস্তেমাল করতে পারি নাই। চাক্ষুষ চলাচল না দেখলে বোঝার উপায়ও নেই। তবে ফেরি দেখে খানিকটা হলেও বোঝা গেল বড়সড় কারবার। যদি কখনো ফেরি চালু হয়, আবার আসার ইচ্ছা রাখলাম।
আবার ফিরতি পথ ধরলাম। পথে দেখলাম নৌকা সংস্কার হচ্ছে। নৌকার ছায়ায় বসে দুজন লোক কাজ করছেন। এই নদী আর নৌকার কারণে বাংলার আলাদা সুনাম ছিল। সেই আদিকালে সন্দ্বীপে বানানো জাহাজ বহির্বিশ্বের নাম কুড়িয়েছে, দিয়েছে পরিচিতি। আর একালে নানা ধরনের জাহাজ তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশের শিপিং ইয়ার্ডে।
ফিরতি পথে তাজ সিনেমা হলের সামনে একটা হোটেলে ঢুকলাম এখানকার ঐতিহ্যবাহী মিষ্টান্ন খেতে। রসমলাইজাতীয় খাবারটির নাম সম্ভবত রসমঞ্জুরি।
গাইবান্ধা শহরের পাশে ঘাঘট নদী। তার পাড় ধরে চলল মিশুক ভাইয়ের মোটরসাইকেল। হালকা বৃষ্টির মাঝে চলছিলাম। আকাশে উঠেছে রঙধনু। এ রঙধনু অনেকটা পথ আমাদের সঙ্গ দেবে। এবার যেখানে এলাম, তার নাম মীরের বাগান। না, এটা কোনো বাগান নয়, মাজার শরিফ। সাথে মসজিদ।
মীরের বাগান নিয়ে একটা গল্প আছে। প্রায় ১২৫ বছর আগে পুরান ঢাকা থেকে কারি করিম বকস এ অঞ্চলে এসে হাজির। স্বপ্নে দেখেছেন, এখানে একটি মাজার ও মসজিদ আছে। সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। সংস্কার সম্পন্ন হয় ১৩০৭ বঙ্গাব্দে। বর্তমানে তার বংশধররাই মসজিদ ও মাজারের রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে আছেন। সেই গল্প করছিলেন মসজিদের ইমাম, যিনি কারি করিম বকসের বংশধর।
এক কাতারের ছোট মসজিদ। গম্বুজ আছে। কোরআনের আয়াত, কলেমা, লতা-পাতার ডিজাইন দিয়ে সাজানো। বোঝা যাচ্ছে, কত কম মুসল্লি আশা করা হচ্ছিল তখন। এখন অবশ্য ছোট টিনের বারান্দাও আছে। দেখার মতো জিনিস হলো আজান দেয়ার স্থানটি। মসজিদের বাইরে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে মিনারের দিকে, যার নিচে নারীদের নামাজের স্থান।
মাজারের ওপর তিনজন ওলির নাম লেখা আছে— পীর শাহ সুলতান গাজী, মীর মোশাররফ হোসাইন ও শরফ উদ্দিন হোসাইন। একই জায়গায় লেখা আছে, মসজিদটি স্থাপিত হয় ১০১১ ইসাই সনে। অর্থাৎ সংস্কারের সঙ্গে ব্যবধান কয়েকশ বছর। মসজিদের সামনে একটা কূপ আছে। এখন হেজেমজে গেছে। এটার তারিখও ১৩০৭ বঙ্গাব্দ।
দুই.
গাইবান্ধা সদর থেকে সুন্দরগঞ্জ বেশ দূরেই। ৩০-৪০ কিলোমিটারের মতো পথ। বাসে বা অন্য কোনো বাহনে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মিশুক ভাই একা ছাড়বেন না। আমাদের জন্য সুবিধাই হলো। অন্য গাড়িতে গেলে অনেক সময় লাগত।
ঘণ্টাখানেক পর আমরা পৌঁছে গেলাম। সুন্দরগঞ্জ বেশ বড়সড় বাজার। এর খ্যাতি অনেক আগে থেকে। নামকরণ নিয়েও আছে কিংবদন্তি। তখন ছিল পাটের মৌসুম। পাটের বিকিকিনি চলছে। বড় বড় ট্রাকে করে পাট যাচ্ছে এখন থেকে। ঘাট খুঁজে পেতে বেগ পেতে হলো। কারণ আগের ঘাট সরে গেছে। নদীর চঞ্চল স্বভাব শুধু নদীকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে না, সাথে সাথে তীরবর্তী জনপদকেও তার ধকল সইতে হয়। নদীর স্বভাবের রেশ ধরে পরিবর্তন হয় ঘাট। পুরনো ঘাট হারায় জৌলুশ। কত কত ঝক্কি তৈরি করে নদী। তার পরও নদীর সঙ্গে মানুষের প্রেম তুলনারহিত। মানুষ যে নদীর মতো ফলবান হতে চায়, এগোতে চায় পরম আরাধ্য কোনো লক্ষ্য ধরে।
বেশ মায়া মায়া একটা বিকাল। হালকা বৃষ্টির কারণে বাতাস ঠাণ্ডা। কিন্তু নদীর পাড়ে এসে ততটা ভালো লাগল না। এটা তিস্তা! এত সরু! কোনো কোনো খালও এত বড় হয়। স্বভাবতই এর চেয়ে বড় কিছু আশা করছিলাম। এসব যখন ভাবছিলাম, তখনো সাথে ছিল রঙধনু। এখানে আরো স্পষ্ট ৯০ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠে গেছে। আর নদীর শান্ত জলে তার ছায়া পড়ে প্রায় ১৮০ ডিগ্রি রূপ নিয়েছে। অভিভূত হওয়ার মতোই দৃশ্য। এই ফাঁকে জানা গেল, এটা মূল তিস্তা নয়। শাখা নদী। সন্তুষ্ট হলাম।
নৌকার ইঞ্জিন স্টার্ট হতে শান্ত নদীর জলে ঢেউ উঠল। কানায় কানায় ভরপুর যাত্রী। এক দলে আছে কয়েকজন নারী, কিশোর-কিশোরী ও শিশু। এর মধ্যে এক কিশোরীর ভাবসাব আলাদা। মনে হলো, তার আউটফিট এর জন্য খানিকটা দায়ী। চুলের রঙ পাটের মতো উজ্জ্বল। কোথাও ধূসর। সোনালি রঙের পোশাক। পায়ে হিল। এ হিল নিয়ে পরে বিপত্তিতে পড়ে। সম্ভবত কোনো অনুষ্ঠানে বেড়াতে যাচ্ছে দলটি।
বিকালকে বিদায় জানাতে জানাতে আমরা এগোচ্ছি। স্নিগ্ধ দৃশ্য দুই পাড়ে। ছোটবেলায় যেভাবে পাড়ের ছবি আঁকতাম সেই রকম। এখন বুঝছি যে, লম্বালম্বি দাগ কেটে পাড় আঁকতাম, সেটা মূলত মাটি ক্ষয়ে যাওয়ার দাগ। সেই দাগটা আঁকা সহজ, কিন্তু তার পরিণতি সহজ নয়।
নদীর পাড়, ফসলের ক্ষেত, আকাশের রঙের সঙ্গে পাল্টানো জলের রঙ, রঙধনু, তার প্রতিবিম্ব, দু-একটা পাখি উড়ছে আর হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়া লোকজন। ইঞ্জিনের শব্দটা এ দৃশ্য থেকে ছেঁটে দিতে পারলে হয়তো গভীর নৈঃশব্দ্যের ধ্যান ধরা পড়ত। তার পরও দেখা গেল, শব্দটা একসময় সহনীয় হয়ে আসে আর এ নীরবতার ধ্যানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। কারো কথা বলার ইচ্ছে তেমন জাগে না। আমরাও কথা বলছিলাম না। মাঝে মাঝে ছবি তুলে নিচ্ছিলাম। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল দু-একটি ইঞ্জিনের নৌকা। আরো বড় ঢেউ উঠছিল। নৌকা দুলছিল। আমরাও দুলছিলাম।
একসময় এই পথ ছেড়ে আরো সরু একটা প্রণালি ধরল নৌকা। এটি খালজাতীয় কিছু! দুই পাশ থেকে বাঁশের মাথায় ঝুলানো জাল পথ আটকে ছিল। নৌকা ঢুকতেই ওপরের দিকে জাল উঠে গেল। যেন টেমস নদীর ব্রিজ। আর দিক পরিবর্তনের কারণে দীর্ঘসময় সঙ্গ দেয়া রঙধনু তাদের সামনে থেকে পেছনে সরে গেল। এই পথে এগোতে এগোতে অনেক মানুষের দেখা মিলল। তারা কাজ সেরে নাইতে এসেছে। নারীদের সাথে বাচ্চারাও আছে। নারীরা চুপচাপ গোসল সেরে নিচ্ছে আর বাচ্চা মেতেছে দুরন্তপনায়। পাড়ে সুন্দর করে আঁটি বাঁধা পাটখড়ি। ঠিক যেন ছোট ছোট পিরামিড। এভাবে চলতে চলতে একসময় পথ শেষ হয়ে আসে। এখানে জলপথ শেষ। অবাক ব্যাপার। কাছেই কি কুড়িগ্রাম?
নৌকার মাঝি ভাড়াও নিলেন না। একজন জানালেন, পথ শেষ হয়নি। কিছুদূর হেঁটে গিয়ে আরেক নৌকা ধরতে হবে। সেখানেই ভাড়া। কিছুক্ষণ মেঠো পথে হাঁটা। একটা রাস্তা পার হতে আবার তেমন সরু জলপথ। মনে হলো, পুরোটাই একটা প্রণালি। মাঝখানে মাটি ভরাট করে রাস্তা বানানো হয়েছে। নাকি ওই রাস্তাটা শেষ বিকালে একদমই নির্জন। দুই পাশে শনের বন। কোথাও কোথাও আঁটি বাঁধা পাটখড়ি। একদম ছবির মতো। ইচ্ছে হয় সেই পথে হেঁটে যেতে।
রাস্তা থেকে নামতে নামতে দেখলাম, কয়েকজন নারী পানিতে পাট পরিষ্কার করছেন। আরেকটু এগিয়ে গেলে দেখা গেল নৌকা অপেক্ষা করছে। একটু উল্টো যেন। ওই যেন কিছু গাড়ি আছে। না, টিকিট কাটলেন একটা। গাড়িতে চড়ে মাঝে নদী পেরোতে হয় লঞ্চে আবার যেতে হয় গাড়িতে। এ রকমই আরকি।
সূর্য ডুবে যাচ্ছে আর জলের মাঝে তার প্রতিচ্ছবি বাড়িয়ে তুলেছে শোভা। আকাশ থেকে সোনা ঝরছে, জল থেকেও আবির্ভূত হচ্ছে ঢেউয়ের আগায়। মসৃণ একটা রেখা এঁকে নৌকা সরে যাচ্ছিল। একটা কলার ভেলায় পার হয়ে গেলাম। আরো এগোতে বিস্ময় খেলে! দূরে দেখা যাচ্ছে। ওই তো তিস্তা! আর অন্য নদীর মতো তিস্তার সন্ধ্যা দীর্ঘ হয়। অনেকটা সময় মেলে ধরে অন্ধকারে অদৃশ্য হওয়ার আগের রূপের বাহার। আমরা এগোতে থাকি তিস্তার দিকে।
ভরা বর্ষার পর আমরা এসেছি। এখন শরত্কাল। এখনো ফুরসত মিললেই আকাশ বৃষ্টি ঝরায়। নদীতে কূল প্লাবিত করা থৈ থৈ জল। সব দিকেই ভাঙনের চিত্র। পুরো দুনিয়া গাঢ় সোনালি রঙে ডুব দিয়েছে। মোহনায় কিছু নৌকা চোখে পড়ল। বাড়ি ফিরছে তারা। মাছ ধরার ব্যতিব্যস্ততা নেই। কখন মাছ ধরে এরা? আমার জানা নাই। পদ্মা নদীর জেলের মতো এখানেও কুপি, হারিকেন জ্বালিয়ে রাতভর মাছ ধরে? এখন অবশ্য কুপি বা হারিকেনের যুগ না, পাওয়ার ব্যাংক, চার্জ লাইটের যুগ। এরও কয়েক মাস আগে বরগুনার তালতলীতে দেখা হয়েছিল ইলিশ মাছ ধরে, এমন কয়েকজন জেলের সঙ্গে। জানিয়েছিল, জলের জীবন আগের মতো নিস্তরঙ্গ না। তারা এক-দুই সপ্তাহের জন্য চলে যান, সাথে নেন মোবাইলসহ নানা অনুষঙ্গ। অবসরে সিনেমাও দেখেন। তবে হ্যাঁ, সি সিকনেস ব্যাপারটা আগের মতোই আছে।
তিস্তা কি সেই বিরল নদীগুলোর একটি নয়! যার নামে উপন্যাস আছে ‘তিস্তাপাড়ের বৃত্তান্ত’। অবশ্য সে গল্প এ জনপদের নয়, আরো উজানের। তবুও নদী-মানুষের লীন হয়ে থাকার আনন্দ-বেদনার একটা বিমূর্ত ছবি কল্পনা করা যায়। স্থান-কালে অনেক অদলবদল ঘটেছে, নদী তার পুরনো সে াত হারিয়েছে, হয়তো মরেও গেছে, নামও পাল্টেছে। নদীর সূত্র ধরে সভ্যতার রকমফের ঘটেছে। কিন্তু মানুষ আর নদীর সম্পর্কের চেহারা অক্ষয়। এটা অতিশয়োক্তি হতে পারে। কিন্তু চিরকালই তো ‘নদী’ শুনলে বুকের ভেতর কেমন যেন করে। কেন? বহমানতাকেই জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে আমরা জগজ্জীবনের মন্ত্র ধরে রেখেছি। এভাবেই মানুষের বিকাশ, অনাঘ্রাতা কুসুম ছড়িয়েছে সুবাস।
এপার থেকে ওপার দেখা যায় না, নদীর বিস্তৃতি এমন। আমরা কূলের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। ওই পাশে ফসলের মাঠ। মাঝে মাঝে লম্বা বৃক্ষ বা বাড়ি ফেরতা মানুষজন চোখে পড়ছে। কোথাও নিঃসঙ্গ নৌকা। যাত্রীভর্তি নৌকা। সন্ধ্যার রঙের ভেতর একটা মিতালি পেতেছে সবাই। কারো যেন আলাদা রঙ নেই। ধীরে ধীরে মাঝনদীতে এসে পড়ে নৌকা। ভয় লাগে বুঝি। হঠাৎ হঠাৎ ভুস করে জল থেকে বুদ্বুদ ওঠে। ভীষণ আলোড়ন জাগে। ওই বুঝি কোনো জলদানব নিঃশ্বাস নিল। উঠে আসবে কি?
মানুষের আত্মা প্রকৃতির ধর্ম বুঝতে পারে। মনের ভেতর কত কথা আসে-যায় করছে, কিন্তু কিছুই কইতে ইচ্ছে করে না। নৌকার সবাই চুপ। বাচ্চাগুলোও। যেন কৌতূহলশূন্য, গন্তব্যহীন একদল অভিযাত্রী ছুটে চলেছি। এ কথাগুলো যখন বলছি, তখন আবার ভাবছি, এ বাসনা শুধু আমার। অন্যের মনকে জানা যায় না। যদি যেত জগত্টা কেমন হতো? আরো সরল নাকি জটিল?
হিন্দু পুরাণ অনুসারে দেবী পার্বতীর স্তন থেকে উত্পন্ন হয়েছে তিস্তা। আর বাংলা নাম তিস্তা এসেছে ‘ত্রি-স্রোতা’ বা ‘তিন প্রবাহ’ থেকে। তিস্তা নদী আগে জলপাইগুড়ির দক্ষিণে তিনটি ধারায় প্রবাহিত হতো; পূর্বে করতোয়া, পশ্চিমে পুনর্ভবা ও মধ্যে আত্রাই। সম্ভবত এ তিনটি ধারার অনুষঙ্গেই ত্রিস্রোতা নামটি এসেছিল, যেটি কালক্রমে বিকৃত হয়ে দাঁড়ায় তিস্তা। তিনটি ধারার মধ্যে পুনর্ভবা মহানন্দায় মিশত। আত্রাই চলনবিলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে করতোয়ায় মিশত। তারপর আত্রাই-করতোয়ার যুগ্ম ধারাটি জাফরগঞ্জের কাছে মিশত পদ্মায়। ১৭৮৭ সালের এক বিধ্বংসী বন্যার পর তিস্তা তার পুরনো খাত পরিবর্তন করে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদে গিয়ে মেশে। এসব তথ্য নিলাম উইকিপিডিয়া থেকে। আর মানচিত্রে দেখে নিতে পারেন, যেখানে তিস্তা আর ব্রহ্মপুত্র মিশেছে তার বিশালতা আর বুকে উঁকি মারছে চর।
তিস্তা প্রসঙ্গ এলে উপমহাদেশের পানি নিয়ে শোষণের অধ্যায়টা কোনোভাবেই বাদ দেয়া যাবে না। নদীর ওপর নদীতীরবর্তী মানুষের অধিকার প্রাকৃতিক। কিন্তু উজানে বাঁধ, পানি প্রত্যাহারের কারণে সে অধিকার লঙ্ঘিত হয়ে আসছে অনেক বছর ধরে। এ নিয়ে চুক্তি ও নানা কথা শোনা যায়। ঘটনা এমন, যেন অধিকারকে অন্য কিছুর বদলে পেতে হবে। তাও যদি উজানের দেশের দয়া হয়! ভাগ্যিস, এখন বর্ষা হওয়ায় সেই রূপ দেখতে হলো না।
বাংলাদেশেও বাঁধ আছে। কৃষি ও সেচের জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখান থেকে আরো উজানে লালমনিরহাটে বিখ্যাত তিস্তা বাঁধ। আরো দুদিন পর ওই বাঁধের ওপর দিয়েই আমরা নীলফামারী ঢুকব। পরে ঝড়ের মুখোমুখি হব ওই বাঁধের কারণে সৃষ্ট কৃত্রিম খালের পাড়ে। আরো মজার বিষয় হলো, সেই খালের নিচ দিয়ে আড়াআড়ি বয়ে গেছে একটা ছোট নদী। সে গল্প আপাতত থাক।
নৌকা উলিপুর পর্যন্ত যাওয়ার কথা। কিন্তু তার অনেক আগেই বলল, আর যাবে না। আমাদের সবাইকে বিস্তীর্ণ ফসলের ক্ষেতের পাশে নামিয়ে দিল। সরু আল ধরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। নদী আস্তে আস্তে ছবির মতো স্থির হয়ে হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। অনেকটা এসে খালের ওপর ছোট্ট একটা কাঠের পুল পার হতে হয়। তারপর সামান্য সময়ের জন্য নৌকা। রাস্তায় উঠে শেষবারের মতো তাকালাম নদীর দিকে। চোখের ভেতর পুরে নিলাম সেই রঙ, সেই দৃশ্য, যার বর্ণনা থাকুক সঙ্গোপনে।
এক ভদ্রলোক আমাদের আশ্বস্ত করলেন, উলিপুর যাওয়ার গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেবেন। তিনি একজন কৃষক। কোনো একটি কাজে এ পাড়ে এসেছেন। যাত্রাপথে এমন অনেক মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি। এ যেন নদীর স্রোত। সর্বদা সে অজানা-অচেনাকে নিজের রূপ দেখিয়ে যায়। আপন করতে চায়। আর ভাঙনের চেয়ে মানুষ বেশি মনে রাখে গড়াকে।
লেখাটি বণিক বার্তার শুক্রবারের আয়োজন সিল্করুটে প্রকাশিত।