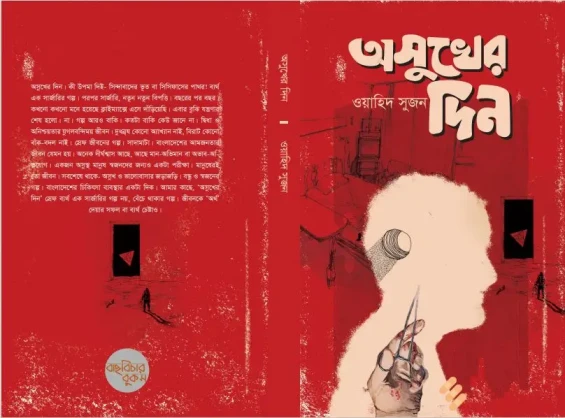এক.

বাংলা সিনেমার ইতিহাসে আলমগীর কবিরের মতো চরিত্র একটাই। শুধু চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে নন, রাজনৈতিক সক্রিয়তা ও সাংবাদিকতার বিবেচনায় বিপ্লবী তিনি। কবিরের সিনেমায় আসার অনুপ্রেরণা ছিল ১৯৬০ এর দশকে দেখা ইঙ্গমার বার্গম্যানের ক্ল্যাসিক ‘সেভেনথ সিল’। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় জহির রায়হানের তত্ত্বাবধানে আবির্ভূত হন প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা হিসেবে। যুদ্ধ শেষে পুরোদস্তুর ফিচার ফিল্মের নির্মাতা বনে যান। একে একে নির্মাণ করেন রূপালী সৈকত, ধীরে বহে মেঘনা ও সীমানা পেরিয়ে।
আলমগীর কবিরকে নিয়ে কথা তোলার উপলক্ষ তার লেখা বই ‘ফিল্ম ইন বাংলাদেশ’-এর অনুবাদ ‘বাংলাদেশে চলচ্চিত্র’। নাজিয়া আফরিনের অনুবাদ প্রকাশ করেছে কিউরিয়াস ঢাকা। বইটির প্রকাশকের ভাষ্য, “চলচ্চিত্রাচার্য আলমগীর কবিরের ‘ফিল্ম ইন বাংলাদেশ’ বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে। ইংরেজি এই বইটি ঐ বছর পর্যন্ত তো বটেই, সম্ভবত আজ এই ২০১৮ সাল পর্যন্তও বাংলাদেশের জাতীয় চলচ্চিত্রের উদ্ভব ও বিকাশ বিষয়ে একমাত্র গ্রন্থ। আলমগীর কবির কেবল একজন সু-নির্মাতাই ছিলেন না, ছিলেন স্বতন্ত্র শিল্প-মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রকে জানা বিরল এক লেখক।”
দেশীয় চলচ্চিত্রের উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে হয়তো একমাত্র বই নয়। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে স্থানীয় চলচ্চিত্রের হাল-হকিকত দরকারি নাও হতে পারে। বরং মূল বইটি প্রকাশের চার দশক পরও বাংলাদেশের সিনেমার ভাষা কী হবে এই প্রশ্ন হররোজ শোনা যাচ্ছে। আলমগীর কবিরের সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ, প্রস্তাবনা ও অনুমান আছে এ প্রসঙ্গে। জানতে পারি চলচ্চিত্রকে জাতীয়করণের একটা
প্রস্তাবনা এসেছিল জহির রায়হানের (পৃষ্ঠা ৬২) নেতৃত্বে। তবে তা স্বাধীন দেশের শুরুতেই হোঁচট খায়। সেটা ভালো বা মন্দের তর্ক ছাড়াই আমরা দেখেছি অন্যান্য ক্ষেত্রে অতি উৎসাহী আধখ্যাঁচড়া জাতীয়করণ সফল হয়নি। অনেক খামতির আলোচনা শেষে এই বইয়ে আমরা দেখি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রের ধারণা। যা আজও আরাধ্য। কিন্তু যার কল্পনা যে বিরল নয়, তার উদাহরণ আলমগীর কবিরের এই বই।
দুই.
সাধারণত বাংলাদেশি সিনেমাকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। মূলধারা ও স্বাধীন ধারা। হ্যাঁ, এই নিয়ে বিতর্ক আছে। আজকাল ভালো-মন্দও বলে অনেকে। মুশকিলের বিষয় হলো দুই ধারার নির্মাতারা পরস্পরকে জানা-বোঝা থেকেও নিজেদের বিরত রেখেছেন। তাই স্থানীয় চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের প্রশ্নও অস্পষ্ট তাদের মাঝে। হয়তো ওই জায়গায় কবির গুরুত্বপূর্ণ। নোকতা আকারে বইটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল। যেখানে ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে নতুন পথের দিশা চাইছেন।
বইয়ের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম ‘পূর্ববাংলার চলচ্চিত্র : ঐতিহাসিক বিবরণ (১৯৪৭-৭০)’। কবির এখানকার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ও পাঠাতন নিরূপণে অনেকটা সময় ব্যয় করেছেন। প্রথম খণ্ডের শুরুর অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় হলো- বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার ঐতিহাসিক কারণ বা দেশভাগের পরের সিনেমায় মঞ্চনাটকের ঐতিহ্য। যদিও খোদ ‘সংস্কৃতি’ বিষয়টাই স্পষ্ট নয়। বিশেষ করে যে মুসলমানের সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা নিয়ে একপ্রস্থ লিখেছেন তাদের ঘরের খোঁজ তেমন পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় না বাংলা সংস্কৃতির বিকাশের সুলতানি আমলের ভূমিকা। আবার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন ঔপনিবেশিক আমলে অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে সুযোগ-সুবিধার নগদ আদায়ে কতটা পিছিয়ে ছিল মুসলমানরা। পরবর্তীকালে কলকাতাকেন্দ্রিক শিল্প-বাণিজ্যের ভিড়ে মুসলমান নাম-ডাক ছিল আচ্ছুদ। তা সত্ত্বেও পূর্ব বাংলায় কলকাতার আছর বরাবরই ছিল। এখানকার সিনেমা যেন কলকাতায় বিকশিত মঞ্চনাটক!
তিন.
দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসেছে স্বাধীনতাপূর্ব আমলের (১৯৫৬-৭০) সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ। যেখানে ‘মুখ মুখোশ’-এর কাল ধরে আদর্শ নারীর মহিমা, হারানো সুযোগ ও ব্যর্থতার কারণ নামে আলোচনা করা হয়েছে। আজকাল যে স্টিরিওটাইপ বাংলা সিনেমার আলোচনা হয় সেই একই আলোচনায় ভারাক্রান্ত কবির। আবার সীমিত সুযোগ ও নির্মাণের ভেতরে দেখতে পেয়েছিলেন সম্ভাবনা।
পূর্ব বাংলায় উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে পরে সিনেমা শুরু হয়। তাই সর্বশেষ প্রযুক্তিতে হালনাগাদ থাকার পাশাপাশি নির্মাণে নতুনত্বের সুযোগ ছিল। সুযোগ ছিল নিজস্ব গল্প বলার। কিন্তু নানা কারণে তা আর সম্ভব হয়নি। তারপরও বইটির পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে দেখা যাবে ঊনিশ শ সত্তরের দশকের প্রেক্ষাপটে নিজস্ব চালচ্চিত্রিক ভঙ্গি নিয়ে কতটা আশাবাদী ছিলেন কবির। আবার জহির রায়হান বা ফতেহ লোহানীর মতো নির্মাতা যখন প্রথাগত ধাঁচ থেকে বেরোতে যান সিনেমার গল্পের নিজস্বতা ও দর্শক আকর্ষণের দিকগুলো স্পষ্ট করতে না পারায় একইসঙ্গে শৈল্পিক ও বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়েছে। কৌতূহলোদ্দীপক মন্তব্য আছে এ জে কারদারের ‘জাগো হুয়া সাভেরা’ নিয়েও। তার মতে, এ অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সময় না কাটিয়ে সিনেমাটি নির্মিত হয়েছে। তবে ‘তৎকালীন পাকিস্তানে এটাই দক্ষ চলচ্চিত্র নির্মাণের একমাত্র উদাহরণ’ (পৃষ্ঠা ৫২) ।
চার.
দ্বিতীয় খণ্ডের শিরোনাম ‘বাংলাদেশের চলচ্চিত্র : ঐতিহাসিক বিবরণ (১৯৭১-৭৫)’। এর মধ্যে স্থান পেয়েছে স্টপ জেনোসাইড ও অন্যান্য যুদ্ধকালীন চলচ্চিত্র এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রযোজনা। পরে যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র, নকল চলচ্চিত্র ও ভিন্নধারার চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচিত হয়েছে এই সময়কালের ‘সমালোচনামূলক চলচ্চিত্র’-এ। এসেছে প্রযোজনা, বাণিজ্যরীতি ও চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের প্রসঙ্গ।
এই বইয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও ব্যর্থতা এই যে, আলমগীর কবির যে সব সমস্যার দিকে আলো ফেলেছেন তা তেমনই সমস্যা আকারেই রয়ে গেছে। সঙ্গে জমেছে আরও জঞ্জাল। আর ব্যর্থতা আলমগীর কবিরের নয়, সামগ্রিক ব্যর্থতা। তার শুরু হয়তো রাষ্ট্র গঠনের মাঝেই আছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে আদর্শগত রাজনৈতিক ভাবধারার জাতীয় চলচ্চিত্রের নীতি পাওয়া যায় বইয়ে। তবে কিছু ব্যর্থতার সঙ্গে আলমগীরের কবিরের ক্ষোভ ছিল যথার্থ। অন্তত মুক্তিযুদ্ধের আখ্যানকে সিনেমার বড় ক্যানভাসে তুলে ধরার ব্যর্থতা। যেখানে বাণিজ্যিক লাভ-ক্ষতির বিষয়ের পাশাপাশি আছে যুদ্ধের ছবি নির্মাণে যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকা ব্যক্তিদের এগিয়ে আসা। এমনকি পরের দশকগুলোতেও মুক্তিযুদ্ধের আখ্যান নিয়ে কোনো পরিপূর্ণ চলচ্চিত্র পাওয়া যায় না।
পাঁচ.
বইয়ের তৃতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায় ‘চলচ্চিত্রের ভাষা এবং বাংলাদেশের চলচ্চিত্র’। আলোচিত বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অপ-চলচ্চিত্রের পরম্পরা, বিশুদ্ধ চলচ্চিত্র কী, শৈল্পিক চলচ্চিত্রের জন্য যা জরুরি, তথ্যচিত্র ও পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে সম্পর্ক এবং পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র সম্পর্কিত ধারণা। মূলত, ধাপে ধাপে ইতিহাস পরম্পরা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে চলচ্চিত্র সম্পর্কিত নিজস্ব সংজ্ঞায় হাজির হয়েছেন তিনি। যা তার সিনেমায়ও দেখা যায়।
তথ্যচিত্র ও পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের ফারাক ঘুচে যাওয়ার বর্ণনা বেশ আকর্ষণীয়। এই ভাবনাটা ফলপ্রসূ হলে আক্ষরিক অর্থেই বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অনেক দূর এগিয়ে যেত। সামগ্রিকভাবে বলছেন, ‘পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রের উত্থান মানেই এতকাল ধরে কাহিনী-সৃজনে অত্যাবশ্যক হয়ে থাকা কল্পনাশক্তির অবসান নয়। কল্পনাকে এখানে সূক্ষ্মভাবে আলাদা একটি ভূমিকায় নিযুক্ত করা হবে; নির্বাচন এবং আয়োজনের কাজে। যদি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য হয় সত্যকে তুলে ধরা, তাহলে বোধ এবং কল্পনার দায়িত্ব হবে বাস্তবের আবর্তের ধাঁধাময় বিশৃঙ্খলা থেকে সত্যকে ছেঁকে বের করা; কারণ সত্যমাত্রই বাস্তব কিন্তু বাস্তবতার গোটাটাই সত্য নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে নির্মাতা বা Auteur অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি করেন তার ভূমিকা আগের চেয়ে মহান ছাড়বে না। কিন্তু মানুষের কোনো উদ্যোগই স্ববিরোধমুক্ত হতে পারে না। মানুষের চিন্তা এবং সৃজনশীলতা ক্রমাগত সামনে এগিয়ে গেছে। পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রও এগিয়ে যাবে।’ (পৃষ্ঠা ১১৬)
একই খণ্ডের শেষ অধ্যায় হলো ‘চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা এবং চলচ্চিত্র-সমালোচনা’। এইখানকার উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো চলচ্চিত্র-সমালোচকের ভিত্তি, আবশ্যিক শর্তসমূহ, সমালোচকের সৃজনশীলতা ও বাংলাদেশে চলচ্চিত্র নিয়ে লেখালেখির মান।
আগেরগুলোর মতো এই অধ্যায়টিও কৌতূহলোদ্দীপক। সিনেমা নির্মাণের আগে আলমগীর কবির ছিলেন সাংবাদিক। প্রকাশ করেছেন বিখ্যাত সিনে জার্নাল, প্রতিষ্ঠা করেছেন সিনে ক্লাব। তার কলমের আঁচড়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়েছে স্থানীয় সিনেমা। যার কিছু নমুনা এই বইয়ের আছে। আর এই উপলক্ষে নিজের নির্মাণেও কলমের আঘাত হানতে হয়।
‘বাংলাদেশে চলচ্চিত্র’ মূলত ইতিহাসের ভেতর থেকে আলমগীর কবিরের নিজের দিকে ফিরে দেখা। আর নিজেকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার সাফ সাফ ইশতেহার। এমন ইশতেহার হয়তো সব নির্মাতা লিখবেন না কিন্তু কোথা থেকে এসে তার কোথায় যেতে চান সেটা পরিষ্কার থাকলে বোধহয় আরও সহজ হয়ে ওঠে নিজেকে প্রকাশ। সেই কারণে আলমগীর কবিরের গুরুত্ব আরও বাড়ে।
লেখাটি দেশ রূপান্তর পত্রিকায় পূর্ব প্রকাশিত।