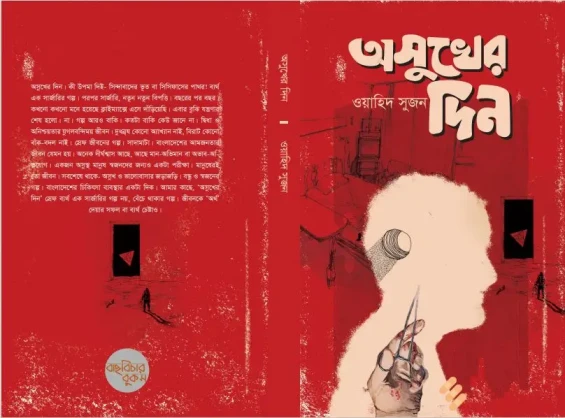চৌধুরী মুঈন উদ্দিন নিয়ে আমার জানাশোনা যে খুব একটা ছিল, এমন না। নামটা জানা ছিল। আরো জানতাম যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী এ ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে ‘যুদ্ধাপরাধের’ অভিযোগ রয়েছে। সম্ভবত সেখানকার চ্যানেল ফোরের বরাতে তাকে নিয়ে একট নিউজ দেখছিলাম ঢাকার টিভি চ্যানেলে। যখন যুদ্ধাপরাধের নামে উইচ হান্টিং চলছিল। সম্ভবত গত বছর ওনাকে নিয়ে পিনাকী ভট্টাচার্যের লেখা পড়ছিলাম। যেখানে বলা হয়, চৌধুরী মুঈন উদ্দিনকে নিয়ে মন্তব্য করায় এক ব্রিটিশ এমপিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এ জানাশোনার মধ্য দিয়ে কাউকে বিচার করা যায় না। এমনকি শুধু তার আত্মজীবনী পড়েও। তা সত্ত্বেও যেকোনো বয়ানের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে।

কয়েক মাস আগে ফেসবুকে এক বন্ধুর পোস্টে উনার আত্মজীবনী থেকে একটা অংশ পড়ি। এরপর বইটার বিজ্ঞাপন সামনে আসতে আরো কিছু বইয়ের সঙ্গে রকমারিতে অর্ডার করি। লম্বা সময় টেবিলে থাকা থাকার পর তিন-চারদিন মিলিয়ে ৩০০ পৃষ্টার বইটা পড়ে ফেলছি। এটা আমার জন্য বেশ দ্রুতই পড়া। বইটার নাম ‘পৃথিবীর গোলাবের বুকে’।
বইটা যে দ্রুত পড়তে পারছি। এমন নয় যে এটা অনেক দরকারি বই, এ কারণে। কারণ হলো, বইটার ভাষা গুণ। এরপর ধীরে ধীরে এর গুরুত্ব ধরা পড়ল। সম্ভবত চৌধুরী মুঈন উদ্দিন (এক সময়) সাংবাদিকতার সঙ্গে থাকায় নির্মেদ-ঝরঝরে একটা ভাষা আয়ত্ত করছেন। পরে কতটা চর্চা করেছেন তা জানি না। তবে তার গল্পটাও বোধগম্য ভাষায় বলার দরকার ছিল। আরেকটা বিষয় হলো তার ছেলেবেলার গল্প। ফেনী-নোয়াখালী মিলিয়ে বর্ণনা; যেখানে সুফি ঐতিহ্য থেকে বের হয়ে আসা একটা পরিবারের গল্প আছে। জমিদার পরিবার। তবে তারা পরবর্তীতে সুফি সিলসিলার ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন নাই। ‘মেঘনার ঢল’ বলে একটা ব্যাপার আছে- এ বইয়ে তার একটা বর্ণনা আছে। মনে মনে বিষয়টা বিশদভাবে জানতে চাইলেও কখনো খুঁজে দেখি নাই। এর আগে বুদ্ধদেব বসুর বালকবেলার স্মৃতিতে কিছুটা পড়ছিলাম।
যাই হোক, সেখানে একটা শব্দ আছে ‘সনতারা’ (জাম্বুরা)। কয়েক বছর আগে গ্রাম থেকে আমাদের এক আত্মীয়া আসছিলেন, সঙ্গে তার নাতনি। ওই মেয়েটা বারান্দায় ডালিম গাছ দেখে সনতারা বলতেছিল, আমরা প্রথমে বুঝি নাই। আরেকটা শব্দ ‘খেসি’, সম্ভবত ‘সম্পর্ক’ বোঝায়। আমার ছোট খালার মুখে শব্দ শুনছি। এই বইয়ে এক জায়গা শব্দটা পাইলাম। মানে হলো, আমার জীবনে ছোট ছোট বিষয়গুলো আকর্ষণ করে।
বইটার এক জায়গায় বলা আছে, জেলা পর্যায়ে কবিতা আবৃত্তিতে চৌধুরী মুঈন উদ্দিন দ্বিতীয় হইছিলেন। আর যিনি প্রথম হইছিলেন তার নাম ফরহাদ মজহার। যাই হোক, আমি বইটার রাজনৈতিক অংশ নিয়ে ছোট আকারে বলব। যেহেতু এ বিষয়ে বিশ্লেষক বা গবেষক কোনোটাই দাবি করার রসদ নাই আমার।
জামায়াত ইসলামীর পলিটিক্যাল ইতিহাস নিয়ে আমার জানাশোনা সামান্য। বিশেষ করে আমাদের ‘মূলধারা’র ইতিহাসে জামায়াত ব্রাত্য অনেকটা। হুট করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের মধ্যে যেন তাদের আবির্ভাব ঘটে। পাকিস্তানের পক্ষে এবং তর্কসাপেক্ষে সেনাবাহিনীর সহায়ক হিসেবে। এ ব্রাত্য অনেকটাই ইসলামপ্রশ্নজনিত। শুধু আমি ভাবছি এমন না, অনেকেই নিশ্চয় ভাবেন যে, ইসলাম বিষয়টাকে অচ্ছ্যুত হিসেবে নিলে জামায়াত ইসলাম নিয়ে আমরা কোনো উপসংহারে আসতে পারব না। তাতে যে জামায়াত না-ই হয়ে যাবে এমনও না। চৌধুরী মুঈন উদ্দিনের বইয়ের আকর্ষণ এই জায়গায়। তিনি আত্মস্মৃতির মাধ্যমে পাকিস্তান ভাগ এবং ছাত্রসংঘের একজন নেতা হিসেবে তখনকার মেজাজটা তুলে ধরতে চাইছেন। সুসম্পাদিত বইয়ের এ অংশটা আরেকটু ডিটেলস হতে পারত।
ধরেন, কয়েক দশকে হইজীবনে তো অল্প-বিস্তর হইলেও জামায়াত-শিবিরের মানুষ দেখছি। রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় সমাজের অন্য একটা অংশ হিসেবে তারা যেমন আমাদের আলাদা করেছেন, আমরাও করছি। অথচ জামায়াত ইসলামী লোকজন কিন্তু জাতীয় সংসদেও গেছে। কেমন যে মূলধারা মনে হয় না তাদের, অথচ চৌধুরী মুঈন উদ্দিনের বইয়ে দেখি, তাদের উপস্থিতিটা এমনই। তিনি বলতে চাইছেন, সংখ্যাগতভাবে যা-ই হোক, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে জামায়াতের একটা মতামত ছিল। গুরুত্ব ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সায়ত্তশাসন প্রশ্নে বোধহয় তাতে ধাক্কা লাগে।
জামায়াত এত ব্রাত্য হয়ে পড়ে কেন সমাজে। কারণ জামায়াত ও ইসলাম লেন্স একাকার করে মানুষকে যেভাবে বিচার করা হয় জামায়াত ইসলাম (অন্য ধর্মীয় পক্ষগুলোতে এমনটা নাই এমন না), তার সঙ্গে এলাই করা কঠিন আরকি!
… এবং তারা একাত্তর প্রশ্নে অন্যদের সঙ্গে নয়, ঐতিহাসিকভাবে নিজেদের মধ্যকার বিরোধগুলো আড়াল করেন। চৌধুরী মুঈন উদ্দিন দাবি করছেন, ২৫ মার্চের গণহত্যা প্রশ্নে যে বিরোধ তৈরি হয়েছিল, তার সূত্র ধরে ছাত্রসংঘ থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। তবে রাজনৈতিক সিলসিলা হিসেবে সমর্থক হিসেবে জামায়াতের সঙ্গে যুক্ত হন; যা নেতৃত্বের পর্যায়ে ছিল না। যেহেতু গোলাম আজমের আত্মজীবনী বাজারে আছে (আমি পড়ি নাই) সেখানেও নিশ্চয় ব্যাপারটা থাকবে— সম্ভাব্য বিচ্ছিন্নতার আশঙ্কায় পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াত সায়ত্তশাসিত সংগঠনে পরিণত হতে পারে এমন একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল মওলানা মওদুদীর সম্মতিতে। অর্থাৎ অখণ্ড পাকিস্তান না থাকার বাস্তবতায় তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কী হতে পারে একটা বোঝাপড়া ছিল। এমনকি ২৫ মার্চের কালো রাতের পর মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে তারা সামরিক জান্তা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলছিল। কিন্তু গোলাম আজমের রেডিও বক্তৃতা থেকে নাকি পুরো পরিস্থিতি পাল্টে যায়। নেতার আবস্থান থেকে পুরো দলের অবস্থান দেখা হচ্ছিল। এখানে এসে চৌধুরী মুঈন উদ্দিন ছাত্রসংঘ থেকে পদত্যাগ করেন বলে দাবি আছে বইয়ে। যেহেতু শুধু বইয়ে থাকা টেক্সট নিয়ে বলছি, তাই ব্যাপারটা এখানে থাক।
পাকিস্তানের সেই জামায়াত ইসলামি আর বাংলাদেশের জামায়াত ইসলামি নিশ্চয় এক না; সেই পাকিস্তানও আর ফিরবে না। এমনকি বাংলাদেশে যেকোনো রাজনৈতিক সম্ভাবনাই এ ভূমিনির্ভর। সেই অর্থে ‘অখণ্ড পাকিস্তানের’ সঙ্গে থাকা বা না থাকার বিষয়টি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের আগে (বা আরো আগে) যে অর্থ তৈরি করত, এখন তা করে না। জামায়াতেরও তেমন মিশন আছে মনে করার কারণ নাই। অন্তত আমার। তাহলে একাত্তর প্রশ্নে জামায়াতের কাঁধে সওয়ার হওয়া ‘প্রশ্ন বা লক্ষ্য’গুলো এখন কী? সেটা কী হইতে পারে তেমন ধারণা সেই বইয়ে থাকলেও ঘটমান বর্তমানে আমরা দেখি না। মানে একাত্তর প্রশ্নে জামায়াত যে অর্থে ফ্যাংশন করে। সে দায় জামায়াত ইসলামীর কিনা সেটা জানি না, মানে একটা পরামর্শ দেয়া বা না দেয়ার বিষয় না। চলমান ইতিহাসে কীভাবে ফ্যাংশন করা যায়, সেটা তাদের ভাবা দরকার। এবং ইসলামফোব বা আজকাল তাদের মুখে ‘বিহারী গ/ণহ/ত্যা’ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় তাদের পক্ষ থেকে তা দিয়েও জামায়াত ইসলামী সম্পর্কিত তর্ক-বিতর্ক নিরসন সম্ভব না। হয়তো জামায়াত ইসলামও ভেবেছিল মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে তাদের পক্ষে সাফ-সুতরো হওয়া সম্ভব, সেটাও যে সম্ভব না তা স্পষ্ট। বরং এটা যে সবপক্ষের জন্য একটা ফাঁদ অনেক আগেই বোঝা হয়ে গেছে।
‘পৃথিবীর গোলাবের বুকে’ উল্লেখিত বিষয়ে আমার পড়া প্রথম বই হিসেবে অনেকগুলো নোকতা আছে। আমার জন্য। আর যারা অনেক অনেক পড়েছেন বা একালে ইন্টারপ্রিটেশন তৈরির দায়িত্বে আছেন, তাদের কাছে আকর্ষণীয় নাও হতে পারে। এটা খুব ক্রিটিক্যাল জায়গা থেকে দেখা তাও না। কিন্তু মনে হইল কিছু কথা বলা যায়। বোধহয়।